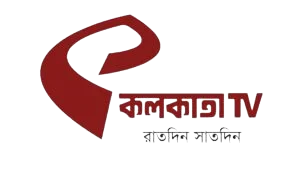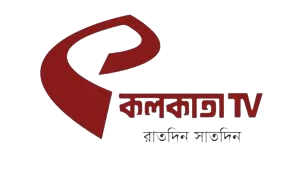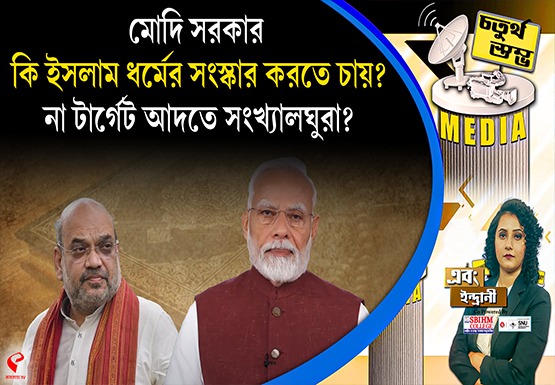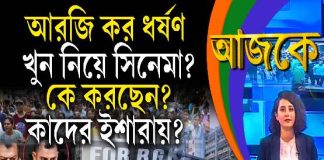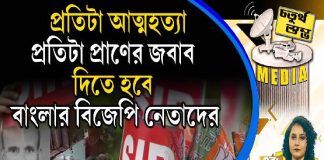আগে একটু বুঝে নেওয়া যাক যে এই ওয়াকফ বিলটা কী আর তা নিয়ে কেনই বা এত বিতর্ক? ওয়াকফ হল ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটা এমন এক ধরনের সম্পত্তি যা কোনও মুসলিম ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় ধর্মীয়, দাতব্য বা জনহিতকর কাজের জন্য স্থায়ীভাবে দান করেন। এই সম্পত্তি গরিব, অভাবী, বিধবা এবং অনাথদের সাহায্য করার মতো বড় আর মহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগে। একবার ওয়াকফ হয়ে গেলে সেই সম্পত্তির মালিকানা আর কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে না, তা সরাসরি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত হয়। ফলে ওয়াকফ আইন অনুযায়ী এই সম্পত্তি কোনওভাবেই বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায় না। ওয়াকফ ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে ধর্মীয়, সামাজিক উন্নয়নের এক প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। এবং সেই কারণেই পৃথিবীতে এই ওয়াকফ সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত নিয়ে বহু দেশে বহু প্রশ্ন উঠেছে, উঠতেই থাকে। কারণ দিন বদলায়, যুগ বদলায় আর পুরনো অনেক ধারণাকে ঢেকে দেয় নতুন চিন্তাভাবনা, এটা নতুন কিছু তো নয়। তবে, এই ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিয়ে বহু দিন ধরেই নানা অভিযোগ ছিল। অনেক সময় দেখা যায়, এই বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। এর ফলে নানা দুর্নীতি আর অপব্যবহারের ঘটনা ঘটতেই থাকে। আর এই সমস্যাগুলোকেই দূর করার জন্য এবং নাকি ওয়াকফ বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সরকার ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ নিয়ে আসে। এই নতুন আইনটার লক্ষ্য ছিল ওয়াকফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং ওয়াকফ বোর্ডকে আরও ক্ষমতা দেওয়া। কিন্তু আইনটাতে কিছু নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, যা নিয়ে বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়। বিশেষ করে, এতে জেলা কালেক্টর এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতটাই বাড়ানো হল যাতে করে এক জেলা কালেক্টর কোনটা ওয়াকফ প্রপার্টি, কোনটা নয় তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে উঠলেন।
আর ঠিক এখানেই মূল সমস্যাটা তৈরি হয়েছে। একদিকে, আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ওয়াকফ সম্পত্তির দুর্বল ব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতি দূর করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে সরকার এমন কিছু নিয়ম তৈরি করেছে যা শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়েই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। অর্থাৎ, এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এই বিল। এটা কেবল এক ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং দেশের এক বিশাল পরিমাণ জমির সঠিক ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গেও জড়িত। আদালতের সাম্প্রতিক রায় এবং চলমান বিতর্ক এই বিশাল সম্পত্তির ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। আসুন দেখে নিই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ঠিক কী বলা আছে? ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৬৪টা পিটিশন জমা পড়েছিল। এই পিটিশনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি আগস্টিন জর্জ মাসিহ-এর একটা বেঞ্চ এই বিলের উপর এক অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করে। সেই রায়ের ফলে বিলটা আপাতত কার্যকর হতে পারবে না বলে বলা হয়েছিল। আদালত বিলের কয়েকটা বিশেষ ধারা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে সেকশন ৩(সি) এবং সেকশন ৪৭ ধারা দুটো নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবারে আদালত এই ধারাগুলোকেই স্থগিত করে দিয়েছে। আদালতের রায়ের মোদ্দা কথাগুলো হল, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক থাকলে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল, হাইকোর্টই মীমাংসা করবে, প্রশাসন নয়। আদালত সেকশন ৩(সি) স্থগিত করেছে। এই ধারা অনুসারে, একটা ওয়াকফ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা জেলা কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছিল। আদালত বলেছে যে, এর ফলে এই ধারাতে ওয়াকফ বোর্ডের বিচার করার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। কারণ, ওয়াকফ বোর্ড হল মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়গুলি দেখাশোনার জন্য তৈরি করা এক বিশেষ সংস্থা। এই বোর্ডের কাজ এক সরকারি কর্মচারীর হাতে দেওয়াটা ঠিক নয়। এর মাধ্যমে প্রশাসনকে (Executive Branch) বিচার করার কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হল। আদালত এখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির (Separation of Powers) উপর জোর দিয়েছে। এটা কেবল একটা আইনি সিদ্ধান্ত নয়, বরং কার্যনির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার উপর বিচার বিভাগের নজরদারি প্রতিষ্ঠা করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | শুভেন্দু, সেলিমের শিক্ষা-দুর্নীতির ইস্যুটা কি ফিকে হয়ে গেল?
আদালত মনে করে, এক ধর্মীয় বোর্ডের সামনে আনা বিষয়ের বিচার করার কাজ সরকারি কর্মচারীর হাতে দেওয়া হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। ২)’নো-ক্লিয়ার রুল’ বাতিল: আদালতের রায়ের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ‘নো-ক্লিয়ার রুল’ বাতিল করা। এই নিয়ম অনুসারে, যদি কোনও সম্পত্তির ওপর ‘কোনও স্পষ্ট নিয়ম’ না থাকে, তাহলে তা ওয়াকফ হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। আদালত এই নিয়মকে ‘বৈষম্যমূলক এবং স্বেচ্ছাচারী’ বলেছে। আদালত বলেছে, এই নিয়মটা ওয়াকফ বোর্ডকে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সম্পত্তির উপর দাবি করার সুযোগ দিত, যা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারত। এই রুল বাতিল করে আদালত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পত্তিকে রক্ষা করার নামে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। এই সিদ্ধান্ত কেবল মুসলিম ওয়াকফ নয়, বরং দেশের সমস্ত ধর্মীয় সম্পত্তির সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত এক বড় নীতিকে তুলে ধরে। ৩) ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যপদ: আদালত বলেছে যে, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যদের অমুসলিম হওয়া উচিত নয়। আদালত মনে করে, এই বোর্ডের মূল দায়িত্ব হল মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়গুলি দেখা। তাই এর সদস্যদের মুসলিম হওয়া আবশ্যক। তবে, এই রায়ের এক অংশ নিয়ে পরবর্তীতে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়। বিশেষ করে, আদালত ‘প্র্যাকটিসিং মুসলিম’ শব্দটার ব্যবহার করে, যা নিয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন যে, ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। মানে কে প্র্যাকটিসিং মুসলিম, কে নয়, সেটা আদালত কীভাবে ঠিক করবে? কাজেই বিভিন্ন জায়গা থেকেই এই রায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা উঠে আসছিল, এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ: ‘ধর্মের অধিকারে নোংরা হস্তক্ষেপ’। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে অনেকেই স্বাগত জানালেও, বেশ কিছু মহলে এই রায়কে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মের অধিকারের উপর এক ‘নোংরা হস্তক্ষেপ’ বলেই মনে করছে। এই অভিযোগটা কেবল আইনি বিষয় নয়, বরং মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে জড়িত। তার প্রথম কারণ ওয়াকফ কেবল সম্পত্তি নয়, এটা এক ‘ঐশ্বরিক আস্থা’ (Divine Trust), ওয়াকফকে কেবল একটা আইনি বা প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে দেখা উচিত নয়। ওয়াকফ হল মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা এক ‘ঐশ্বরিক আস্থা’, যা মুসলিমদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ওয়াকফ আইন কোনও সাধারণ আইন নয়। এটা মুসলিমদের ধর্মীয় আইনের এক অংশ, যা তাদের পবিত্র গ্রন্থ এবং ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত।
আদালত যখন একটা আইনকে বাতিল করে, তখন তা কেবল এক আইনি ত্রুটি দূর করার বদলে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত হানছে বলেও মনে করা হয়। সমালোচকরা বলেছেন, এই আইনটা আদতে মুসলিমদের ধর্মের অধিকারের উপর নোংরা হস্তক্ষেপ। ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা বিচার বিভাগের ক্ষমতার বাইরে। এই একই লজিকে রাম মন্দিরের স্থাপনা হয়, এই একই বিশ্বাসের কথা, ধর্মে আস্থার কথা সেদিন বলা হয়েছে, আজ সেই একই আস্থাকে আঘাত করা হচ্ছে যা সংখ্যালঘু মানুষজনের কাছে এক বড় আঘাত। এর সঙ্গেই সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদ প্রতিটা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অধিকার দেয়। ওয়াকফ বোর্ডকে এই অধিকারের অধীনেই দেখা হয়। ওয়াকফ বোর্ডকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয় হিসেবে দেখা উচিত। আদালত যদিও বিষয়টাকে স্রেফ একটা আইনি দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছে, সমালোচকরা বলছেন যে, এই সিদ্ধান্ত মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত হানছে। তাঁদের মতে, এক মুসলিম ধর্মীয় সংস্থার কাজ-কারবারে সরকারি বা বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ সংবিধানের দেওয়া এই অধিকারের পরিপন্থী। এবং একবার ভেবে দেখুন আদালত ওয়াকফ বোর্ডের জন্য ‘প্র্যাকটিসিং মুসলিম’ শব্দটার ব্যবহার করে আসলে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত, ডিফাইন করার চেষ্টা করছে, যা তার এক্তিয়ারেরই বাইরে। এই ব্যবহারটি বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা (Judicial Activism) হিসেবেই দেখা হবে। আদালতের রায়টা কেবল আইনি ত্রুটি খুঁজে বের করার চেয়েও বেশি কিছু, এটা ধর্মের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা। ঠিক এটাই তো করা হবে না বলে রাম মন্দির জাজমেন্ট-এ বলা হয়েছিল, বিচারবিভাগ ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করবে না, ধর্মকে ডিফাইন করবে না, কিন্তু এখন ঠিক সেটাই করা হচ্ছে।
এই বিতর্কটা আসলে এক গভীরতর আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ। একদিকে, রাষ্ট্র মুখে চায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক আইন এবং স্বচ্ছতার অধীনে আনতে। অন্যদিকে, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও অনুশীলনকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে চায়। আর একদিকে সরকার হিন্দু ধর্ম নিয়ে আরেক মতে বিশ্বাসী, সেখানে তারা ধর্ম এক আস্থার ব্যাপার বলেই ঘোষণা করেছে। এই রায় এই তিন ধরনের মতাদর্শের মধ্যেকার টানাপোড়েনকে প্রকাশ্যে এনেছে। কাজেই এই রায়ের পরেও কেন বহু প্রশ্ন কিন্তু থেকে গেল। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ওয়াকফ বিলের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এই রায় থেকে কয়েকটা মৌলিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, যা এখনও অমীমাংসিত। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই বিতর্ক চলতে থাকবে। প্রথমত, আইন ও ধর্মের মধ্যে মূল দ্বন্দ্বটা এখনও রয়ে গেছে। আদালতের উদ্দেশ্য ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্নীতি রোধ করা। কিন্তু বিরোধীদের মতে, আদালত মুসলিমদের ধর্মীয় স্বশাসনের অধিকারের উপর আঘাত হেনেছে। প্রশ্ন হল, একটি আইনি কাঠামোকে কি ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেখা সম্ভব? যদি না হয়, তাহলে একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কীভাবে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করতে পারে? এই প্রশ্নটা ওয়াকফ আইনের প্রেক্ষাপটে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার জন্যও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, আদালতের উদ্দেশ্য কি সত্যিই সংস্কার, নাকি হস্তক্ষেপ? আদালত ‘নো-ক্লিয়ার রুল’ বাতিল করেছে কারণ এটা বৈষম্যমূলক ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব কেড়ে নিচ্ছে। ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক স্বচ্ছ এবং কার্যকর ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু আদালতের স্থগিতাদেশের ফলে বিলটা আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। এর ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এখনকার সমস্যাগুলো সমাধান হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বরং, এর ফলে এক আইনি শূন্যতা তৈরি হতে পারে, যা আবার ভবিষ্যতে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে। সবশেষে বলি এই ঘটনাটা একটা বৃহত্তর প্রশ্ন তুলে ধরে: এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকারের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব? যখন এক সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের চেষ্টা করে, তখন সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করার জন্য এক ধরনের চাপ তৈরি হয়। এই রায়ের সমালোচনা সেই চাপেরই প্রকাশ। এটা কেবল একটি আইনি সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে এক বৃহত্তর আর জরুরি আলোচনার অংশ। এই আলোচনাটা এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় একটা গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ হলেও, তা ওয়াকফ আইন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বশাসনের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কটা এখনও এক অমীমাংসিত প্রশ্ন হিসেবেই থেকে গেছে।