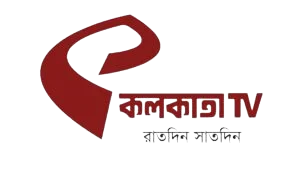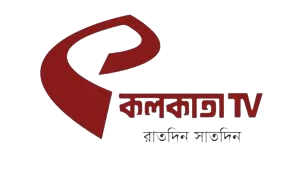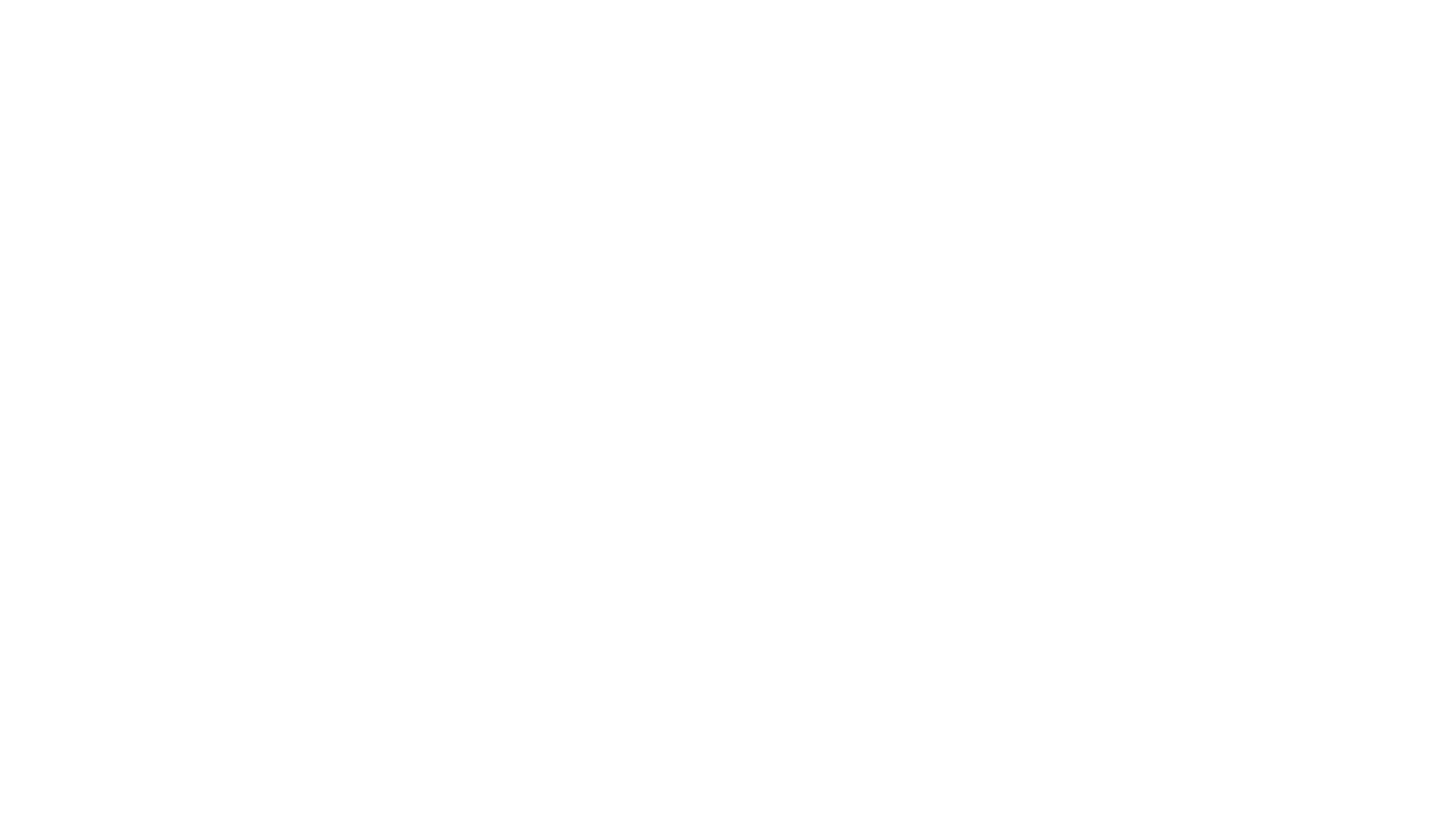ভারতীয় রাজনীতি এক উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর বাড়তে থাকা সক্রিয়তা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনতি আর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দেশজুড়ে এক উত্তাল বিতর্ক চলছে। ঠিক এইরকম এক রাজনৈতিক আবহে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল, ২০২৫ পেশ করেছেন, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বা বলা ভালো বিরোধীরা মনে করছেন, এই দানবীয় বিল আসলে সব প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নেওয়ার জন্যই আনা হল। বাংলাতে এখনই কথা উঠছে যে তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে রাজ্য দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। এই বিলের মূল প্রস্তাবনা সোজা চোখে অত্যন্ত সরল এবং নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্যও বটে, যদি কোনও প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের মন্ত্রী গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে একটানা ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে বা জেলে থাকেন, তবে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে অথবা পদ থেকে অপসারিত করা হবে। সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে তো ৪৮ ঘণ্টা জেল-হাজত হলেই সাসপেনশন অবধারিত, কাজেই নেতা-মন্ত্রীদের তা হবে না কেন? এরকম একটা সরল যুক্তি দেওয়াই যায়।
এই বিল পেশ করার তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপট হিসেবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতার এবং তাঁর জেল থেকে সরকার পরিচালনার নজিরবিহীন প্রচেষ্টার ঘটনাটাকে সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া এই আইন কি শুধুমাত্র সেই শূন্যতা পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষমতার ভারসাম্যকেই চ্যালেঞ্জ করবে? এই বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত অংশটা হল এর মূল প্রস্তাবনা, যা পদের মেয়াদকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। জোড়া হয়েছে ৩০ দিনের শর্ত। বলা হয়েছে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী, কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রী এমন কোনও ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হন, যে অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর বা তার বেশি জেল হতে পারে, এবং তিনি যদি সেই অপরাধের অভিযোগে একটানা ৩০ দিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (custody) থাকেন, তবে তাঁকে পদ থেকে সরে যেতে হবে। ৩১তম দিনে তাঁর পদত্যাগ বাধ্যতামূলক বা তাঁকে অপসারিত করা হবে। মানে মামলার রায় নয়, মামলা চলাকালীন জেল হাজতে থাকলেই চলে যাবে কুর্সি। না, সরকারি কর্মচারীদেরও চাকরি যায় না, কেবলমাত্র সাসপেন্ড করা হয়, চাকরি যায় দোষ প্রমাণ হওয়ার পরে। মানে একজন জনপ্রতিনিধির পদে থাকার অধিকারকে আদালতের চূড়ান্ত রায়ের বদলে তদন্ত প্রক্রিয়ার একটা ধাপের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
মানে এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে অত ঝামেলা করতে হবে না, ইডি-সিবিআই লেলিয়ে দিয়ে কেবল গ্রেফতার করে ৩০ দিনের বেশি জেলে পুরে রাখলেই কেল্লা ফতে। বলা হয়েছে যদি প্রধানমন্ত্রী ৩০ দিন একটানা হেফাজতে থাকেন, তবে তাঁকে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। ব্যর্থ হলে, রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে রাজ্যের রাজ্যপালই মুখ্যমন্ত্রীকে অপসারণ করার ক্ষমতা পাবেন। এখানে তো রাজ্যপাল জো হুজুর বলে সেটা করার জন্য বসেই আছে। দিল্লির মতো বিধানসভা থাকা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীকে অপসারণ করবেন। একইভাবে, রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল অপসারণ করবেন। বিলটাতে একটা সুয়োমোটো রিমুভ্যাল, স্বয়ংক্রিয় অপসারণের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। যদি ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ৩১তম দিনে পদটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য বলে ঘোষিত হবে। তবে হ্যাঁ, বিলকে গণতান্ত্রিক মোড়ক দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, যে মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে এই আইনের অধীনে পদচ্যুত করা হবে, তিনি হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আবার সেই পদে নিযুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে কী হবে? এক নির্বাচিত সরকারের পতনের পর বা রাজনৈতিক সমীকরণ পুরোটা বদলে যাওয়ার পর আবার সেই একই পদে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। ততদিনে টাকার থলে এসে হাজির হবে বারান্দার এক কোণে এবং সব হিসেব বদলে যাবে।
বলা হচ্ছে, বর্তমানে এমন কোনও সুস্পষ্ট সাংবিধানিক বা আইনি বিধান নেই যা দিয়ে গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এবং হেফাজতে থাকা কোনও মন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে সরানো যায়। এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা হলেন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাই তাঁদের চরিত্র ও আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। সেইজন্য ‘সুশাসনের নীতি’ এবং ‘সাংবিধানিক নৈতিকতা’ ফিরিয়ে আনতেই নাকি এই বিল আনা হয়েছে। একটু খেয়াল করে দেখুন, এই বিল কিন্তু ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি— যতক্ষণ না দোষী প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ (innocent until proven guilty), এই নীতির এক্কেবারে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও ন্যাকামি করে প্রধানমন্ত্রীকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে, কিন্তু সত্যিটা হল যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো (যেমন সিবিআই বা ইডি) প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা রাখে, সেগুলো তো কার্যত প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণেই আছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনেই তারা কাজ করে। ফলে, ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই সংস্থাগুলির পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নয় এক্কেবারে শূন্য। কিন্তু বিভিন্ন বিরোধী শাসিত দলের মুখ্যমন্ত্রীদের অবশ্যই গ্রেফতার করতে পারে আর এই বিলের আসল উদ্দেশ্য সেটাই। আর একটা দিকও ভাবতেই হবে ভারতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার এক মৌলিক নীতির হলো ‘অভিযোগ’ (allegation) এবং ‘দোষী সাব্যস্ত’ (conviction) হওয়ার মধ্যেকার পার্থক্য। এই বিলে সেই পার্থক্যকে প্রায় মুছে দিয়ে ‘হেফাজতে থাকা’ বা বিচারবিভাগীয় আটক হলেই তাকে পদ থেকে সরানোর কথা বলা হচ্ছে যা এখনকার আইনি কাঠামোর থেকে বড় বিচ্যুতি। রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায় হল লিলি থমাস বনাম ভারত সরকার (২০১৩) মামলা। এই মামলার রায়ের পর থেকে, কোনও জনপ্রতিনিধি দুই বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য জেল হাজতের শাস্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। লালুপ্রসাদ যাদব, জে জয়ললিতার মতো প্রভাবশালী রাজনীতিবিদরা এই রায়ের কারণেই তাঁদের পদ হারিয়েছিলেন, রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে এই রায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।
কিন্তু এখন রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য শুধুমাত্র একটা মামলা দায়ের করে তাঁকে ৩০ দিন হেফাজতে রাখাটাই যথেষ্ট হবে। কয়েক বছর পর যদি তিনি আদালত থেকে নির্দোষ প্রমাণিতও হন, ততদিনে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বা তাঁর দলের যে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার, তা হয়ে যাবে। এবং পুরো সুযোগটা নেবে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট, দিল্লির সরকার, মোদি-অমিত শাহ। আর সেইজন্যই এই বিল আনা হচ্ছে। যদি পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে দেখব দুনিয়ার বড় বড় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অপসারণের জন্য অত্যন্ত সতর্ক এবং সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়। নিছক ‘হেফাজতে’ থাকার ভিত্তিতেই একজন নির্বাচিত সরকার প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার ধারণাটা কোথাও নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের প্রক্রিয়া হলো ইমপিচমেন্ট (impeachment)। এটা একটা পুরোপুরি আইনসভা-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। প্রথমে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস (House of Representatives) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ইমপিচমেন্টের আর্টিকল বা অভিযোগগুলোকে পাশ করবে। এরপর সেনেটে (Senate) বিচার প্রক্রিয়া চলবে, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে দোষী সাব্যস্ত হলে তবেই তাকে পদ থেকে অপসারণ করা হবে। এবং সেটাও শুধুমাত্র গুরুতর ‘রাষ্ট্রদ্রোহ, ঘুষ, বা অন্যান্য বড় অপরাধ আর অসদাচরণের’ ক্ষেত্রেই এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ব্রিটেনে যদি কোনও সংসদ সদস্য (MP) কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য জেলে যান তবে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁর পদ হারান।
এখানেও ভিত্তিটা হল ‘দোষী সাব্যস্ত’ হওয়া, ‘হেফাজতে থাকা’ নয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ভারতীয় বিল শুধুমাত্র ‘হেফাজতে’ থাকার মতো অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার যে ক্ষমতা রাজ্যপাল বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মতো নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছে, তা বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে বেমানান। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল ভারতীয় গণতন্ত্রকে এক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিলটার পক্ষে সরকারের যুক্তিগুলো খোলাচোখে রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, হ্যাঁ এরকমটাই বলা হচ্ছে, কিন্তু নাগপুরের নির্দেশে যে বিল পেশ করা হল সংসদে তা ভারতীয় গণতন্ত্রের উপরে এক চরম আঘাত, এই বিল পাশ হলে দেশে বিরোধী বলে আর কিছু থাকবে না। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এক পরিকল্পিত চেষ্টা, যখন প্রায় প্রত্যেক দিন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন তাদের হাতে একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার চাবিকাঠি তুলে দেওয়াটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে, ভারতীয় রাজনীতিতে অপরাধ এবং দুর্নীতির প্রবেশ এক গুরুতর সমস্যা, এর মোকাবিলা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক ভারসাম্য আর আইনের শাসনের মূল ভিত্তিগুলোকে দুর্বল করে হতে পারে না। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল যে ভয়ঙ্কর আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে, তা ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিল কোনওভাবেই রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য আনা হয়নি, এক চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা আর প্রতিহিংসার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল এই ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এই বিলটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার জন্য একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে (JPC) পাঠানো হয়েছে। এই কমিটির ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব হবে, বিলটির প্রতিটি ধারার সম্ভাব্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং নিশ্চিত করা যে, রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের নামে যেন গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভগুলিকেই ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। এই বিলটি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা, এবং এর চূড়ান্ত পরিণতিই নির্ধারণ করবে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথ।