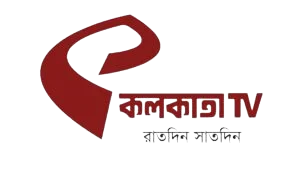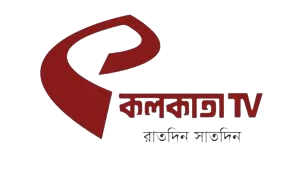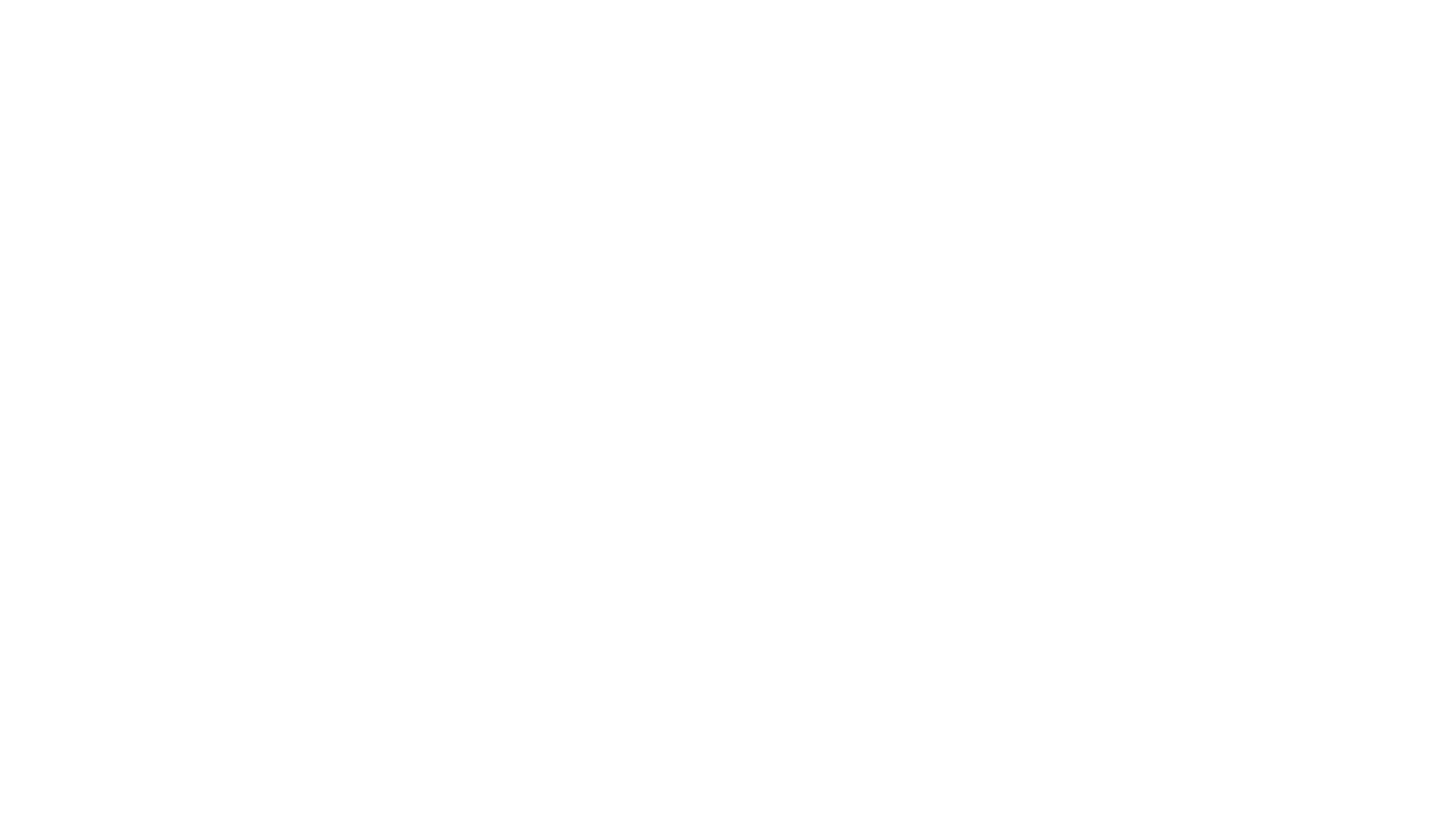নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর আকাশে যখন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল, তখন তা কেবল এক সংসদ ভবনের জ্বলে পুড়ে খাক হওয়ার সাধারণ ছবি ছিল না। বরং ছিল সাধারণ মানুষের বহুদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যা বহু বছরের হতাশাকে এক মুহূর্তে বিস্ফোরণে পরিণত করেছে। নেপালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিক্ষোভে কেবল সংসদ ভবনই জ্বলতে দেখা যায়নি, অর্থমন্ত্রীকে জনরোষের মুখে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়েছে এবং মন্ত্রীদের বাসভবনে হামলা হলে সেনাবাহিনীকে হেলিকপ্টারে করে তাদের সরিয়ে নিতে হয়েছে। এমনকী রাষ্ট্রপতির বাসভবনেও আন্দোলনকারীরা ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ বলে মনে হলেও, এর পিছনের কারণগুলো একটা নয়, অনেক। আর তা গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। এটা মূলত এক বিরাট বেকারত্ব, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের, জেন জি-র এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ।
আসুন দেখে নিই প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন কিন্তু পচে যাওয়া অথচ মানুষের কাছে এখনও শ্রদ্ধেয় রাজতন্ত্রের পতনের পর গণতন্ত্রের নামে নির্বাচিত নেতারা কীভাবে মানুষকে ঠকিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে এই ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম হল। নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল ভিত্তি ছিল শাহ রাজবংশের প্রায় ২৪০ বছরের শাসন। ১৭৬৮ সালে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ নেপালকে এক হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যা নেপালিদের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। এই রাজতন্ত্রে পৃথ্বী বীর বিক্রম শাহ এবং ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহের মতো কয়েকজন জনপ্রিয় শাসকও ছিলেন, এক ধরনের বেনেভোলেন্ট ডিক্টেটর, যাঁরা প্রজাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। নেপালের এক বিরাট অংশের মানুষজন এই রাজপরিবারকে শুধু শাসক হিসেবে দেখত না, বরং দেশের অভিভাবক হিসেবে তাদের জন্য এক ধরনের গভীর আবেগ আর শ্রদ্ধাও ছিল। তারা সত্যি করেই বিশ্বাস করত যে রাজতন্ত্র দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ থেকে দেশকে বাঁচাবে। কিন্তু এই ধরনের স্থিতিশীলতা চিরস্থায়ী হয় না, ছিলও না। ২০০১ সালে রাজপ্রাসাদে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সেই সময়ের রাজা বীরেন্দ্র সপরিবারে নিহত হন। এই ঘটনা নেপালিদের মনে এমন এক গভীর শূন্যতা তৈরি করে যে অনেকে মনে করেন, সেদিনই আসলে নেপালের রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটেছিল। এরপর রাজা হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রর অভিষেক হয়, যিনি জনগণের ততটা ভালোবাসা পাননি।
এই ট্র্যাজেডি এবং পরবর্তীতে মাওবাদীদের এক দশকের গৃহযুদ্ধ রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। একপর্যায়ে ২০০৬ সালে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে রাজা জ্ঞানেন্দ্র এক বহুদলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। অবশেষে, ২০০৮ সালের মে মাসে সংসদীয় ভোটের মাধ্যমে ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং নেপালকে এক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝাটা খুব দরকার, যেখানে সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর জনগণের মধ্যে নতুন ব্যবস্থার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়, পুরনো ব্যবস্থার জন্য থাকে একরাশ ঘেন্না, নেপালের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। রাজতন্ত্রের পতনকে অনেকে এক প্রাচীন ব্যবস্থার অনিবার্য পতন হিসেবে দেখলেও, জনগণের এক বড় অংশের কাছে এটা কিন্তু ছিল তাদের ‘প্রজাপ্রিয়’ রাজপরিবারের শেষ ইতিহাস, যা তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। এই কারণেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তখন জনগণের মধ্যে আবার সেই রাজতন্ত্রের জন্য এক ধরনের ভালোবাসা এবং তার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হয়েছে। তারা মনে করে, রাজতন্ত্রের অধীনে তারা যে স্থিতিশীলতা এবং এক ধরনের অভিভাবকত্ব অনুভব করত, গণতান্ত্রিক সরকার তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নেপালে গেলেই একথাগুলো শোনা যেত, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে এই কথাগুলো উচ্চারিত হত। এই গভীর শূন্যতা এবং মোহভঙ্গই বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম মূল ভিত্তি। একদিকে ২৪০ বছরের শাসন, একই পরিবারের শাসন, অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে নেপালের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? মাত্র ১৭ বছরে দেশটিতে ১৩ বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে, যা নীতি নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব তৈরি করে। এই ঘন ঘন সরকার বদলের কারণে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের জন্য কাজ করার চেয়ে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে বেশি মনোযোগ দিয়েছে।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | মোদিজি = এক প্রকাণ্ড মিথ্যেবাদী
এই সুযোগেই দেশটাতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির শিকড় আরও গভীরে প্রবেশ করেছে, কারণ এখানে দায়বদ্ধতার অভাব ছিল সবার সামনে এক ওপেন সিক্রেট। মানুষজনের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তারা ভোট দেওয়ার ক্ষমতা পেলেও আসল ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে রয়ে গেছে। এই ক্ষোভেরই এক সাম্প্রতিক বহিঃপ্রকাশ ছিল তরুণ প্রজন্মের ‘নেপো কিড’ আন্দোলন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরুণরা রাজনৈতিক অভিজাতদের সন্তানদের বিলাসবহুল জীবন এবং তাদের বিলাসবহুল বিদেশ ভ্রমণের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছিল। এই ডিজিটাল আন্দোলনটা সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং রাজনৈতিক পরিবারের সীমাহীন সুবিধার মধ্যেকার ব্যবধানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। দুর্নীতির এই সংস্কৃতি কতটা গভীর, তার এক বড় প্রমাণ পাওয়া যায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখকের কেলেঙ্কারিতে। ২০২১ সালে তার বিরুদ্ধে এক অভিবাসন কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে, যেখানে বিদেশ যেতে চান এমন নেপালি নাগরিকদের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ ছিল। এমনকী এই কেলেঙ্কারিতে বিদেশে সস্তার শ্রমিক পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগও উঠে আসে। যদিও তিনি সেই সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর নিজের দলের নেতারাও নৈতিক কারণে তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলেন। কিন্তু তিনি তখন পদত্যাগ করেননি, করেছেন গতকাল। এই ঘটনাটা জনগণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি চরম ক্ষোভ আর অবিশ্বাসকে আরও তীব্র করে তোলে। এই ধরনের কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রমাণ করে সেটাই যা সাধারণ মানুষ মনে করে, তাদের ভোটের ক্ষমতা থাকলেও আসল ক্ষমতা কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত পরিবারের হাতেই কেন্দ্রীভূত। এই বিশ্বাসঘাতকতাই বর্তমান বিক্ষোভের মূল কারণ।
তার উপরে জ্বালানি- মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের কষাঘাত এই আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢলেছিল। নেপালের আজকের রাজনৈতিক অস্থিরতার পিছনে অর্থনৈতিক সংকট এক বিরাট বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। চূড়ান্ত বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্বের হার দেশের তরুণ প্রজন্মকে চরম হতাশায় ঠেলে দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, নেপালের বেকারত্বের হার ২০২৪ সালে ১০.৭১ শতাংশ ছিল, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই হার ২০২০ সালের ১২.৯৮ শতাংশ থেকে কিছুটা কম হলেও, দেশের যুব বেকারত্বের হার এখনও ২০.৮২ শতাংশ, যা প্রমাণ করে যে প্রতি পাঁচজন যুবকের মধ্যে একজন বেকার, যারা ভবিষ্যতের কোনও নিশ্চয়তা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। যদিও কাগজে-কলমে নেপালের মূল্যস্ফীতির হার ২০২৩ সালে ৭.১১ শতাংশ ছিল, কিন্তু বাস্তবে ডিম, তেল, ডাল, সবজি এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে একটা ডিমের দাম ভারতীয় টাকায় ১৫ টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ২৫ টাকা হয়েছে। এই অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত মানুষের মনে সরকার আর এই ব্যবস্থার প্রতি চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই প্রতি বছর বিরাট সংখ্যায় নেপালি যুবকেরা উন্নত জীবনের খোঁজে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছে। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির এক বড় অংশ হলেও, এটা একই সঙ্গে দেশের ভিতরে কর্মসংস্থান তৈরির ব্যর্থতার প্রমাণ। যখন একজন তরুণ দেখে যে তার নিজের দেশে কাজের কোনও সুযোগ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের সন্তানদের জীবন বিলাসবহুল, তখন তাদের মনে চরম ক্ষোভ জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক।
এই অর্থনৈতিক হতাশাটাই এই বিক্ষোভের মূল জ্বালানি। সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবল সেই জমে থাকা ক্ষোভের ওপর শেষ স্ফুলিঙ্গ। এই নিষেধাজ্ঞা-বিরোধী আন্দোলন খুব দ্রুত এক বৃহত্তর দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিল। বিক্ষোভকারীরা নিজেরাই স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করা ছিল কেবল এক উপলক্ষ, কিন্তু তাদের মূল ক্ষোভ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনকে ‘জেন-জি বিপ্লব’ হিসেবেও বলছেন তাঁরাই। এটাই প্রমাণ করে যে, সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে আসে। সংসদ ভবন এবং মন্ত্রীদের বাসভবনে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনাগুলো জনগণের আদতে জমে থাকা রাগ আর ক্ষোভের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল। নেপালের এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়, এটা দক্ষিণ এশিয়ার এক বৃহত্তর প্রবণতারই অংশ। শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশে কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পালাবদল নেপালের পরিস্থিতির সঙ্গে মিল চোখে পড়ার মতো। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা ইতিহাসের ভয়াবহতম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছিল। লাগামহীন মূল্যস্ফীতি, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবের কারণেই মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের গণরোষ এত তীব্র ছিল যে তৎকালীন প্রেসিডেন্টকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল এবং সরকারের পতন ঘটেছিল।
বাংলাদেশেও ইনফ্লেশন, ডলার সংকট এবং ব্যাঙ্কিং খাতে ঋণখেলাপিদের বাড়বাড়ন্তের কারণে অর্থনৈতিক সংকট ছিল। তার পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তরুণদের কোটা সংস্কার আন্দোলন এক গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। এই বিক্ষোভের মুখে সরকারের পতন হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই তিন দেশের ঘটনার মধ্যে এক বড়সড় মিল রয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রচলিত সংসদীয় প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যর্থতা যেমন উচ্চ বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি, এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মতো রাজনৈতিক কারণগুলো প্রতিটা দেশেই গণবিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। যখন জনগণ মনে করেছে যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের জন্য কোনও সমাধান দিতে পারছে না, তখন তারা বিকল্প ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে। শ্রীলঙ্কায় বামপন্থী নেতা অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে ক্ষমতায় এসেছেন, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে, আর নেপালে জানা নেই কী হবে তবে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি আরও জোরালো হয়েছে। এই ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, যদি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচলিত গণতন্ত্র জনগণের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং দুর্নীতি দমন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক পালাবদল বা বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বাড়তে পারে। আর তাই নেপালের গণতন্ত্রই এখন এক কঠিন পরীক্ষার মুখে। যদি না এই সুযোগে দেশ আবার রাজতন্ত্রের দিকে হাঁটা দেয় তাহলে নির্বাচিত নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে কেবল বিক্ষোভ দমন করা নয়, বরং জনগণের হারানো আস্থা পুনরুদ্ধার করা। যদি নেপালের নেতারা দুর্নীতিমুক্ত, স্থিতিশীল এবং জনগণের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণকারী এক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সংসদ ভবনের আগুন শুধুমাত্র একটা ঘটনার প্রতীক হয়ে থাকবে না, ভবিষ্যতে এটা দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলোর জন্য এক অশনি সংকেত হয়ে উঠবে।