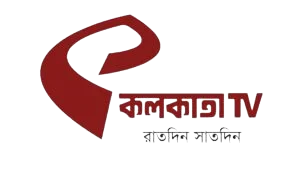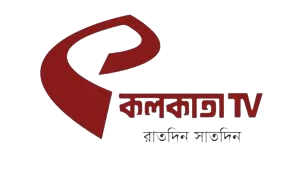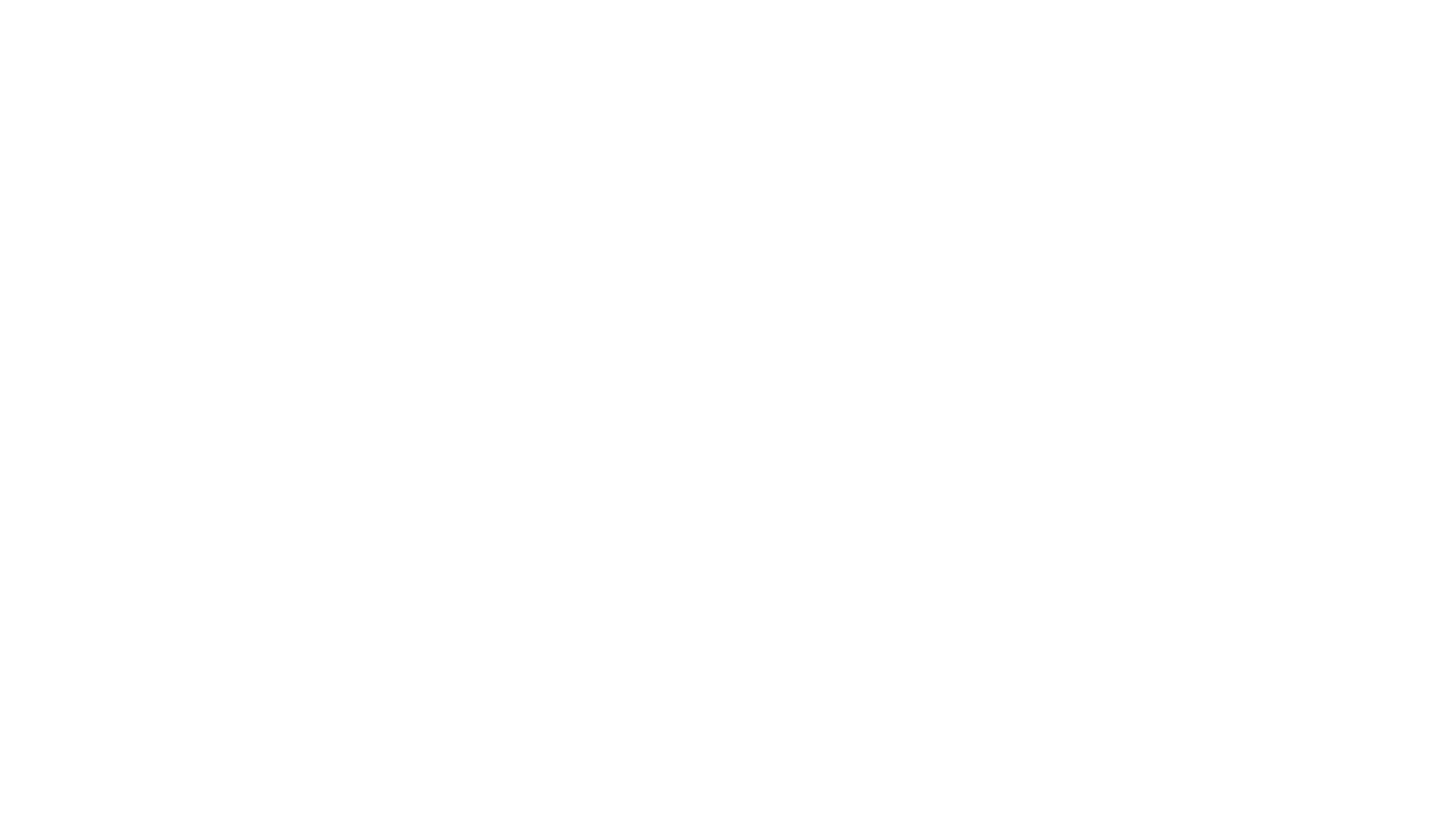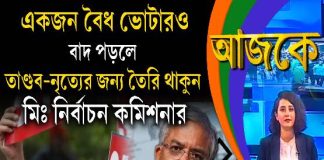এটা ঘটনা যে, ভোট চুরি হয়েছে বিহারে। আর সেটা বললেই সেই মোক্ষম প্রশ্নটা এসে হাজির হবে, ‘তার মানে যেই বিরোধী হারবে, অমনি সেটা চুরি?’ বিরোধীরা জিতলে জণগণের জয়? এবারে আপনি একটু অন্যভাবে দেখুন – আপনি ধানের গোলায় ধান রেখেছেন, ইঁদুর এসে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে মহা আনন্দে, তাদের চুরি চলছে। এবারে আপনি টের পেয়ে গেলেন, কিন্তু তেমন কিছু ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। চুরি চলবে। কিন্তু আপনি একটা বেড়াল পুষলেন, চুরি কি পুরোটা থামবে? তখনও চুরি হবে, কিন্তু অনেক কম হবে। ঠিক সেরকম যেখানে বিরোধীরা জিতছে, সেখানে চুরি হচ্ছে না বা চুরির চেষ্টা হচ্ছে না – সেটা কে বলল? সেখানেও প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু টাকা আটকানো গিয়েছে বলেই বিরোধীরা জিতেছে। হ্যাঁ, এটা হতেই পারে একটা ব্যাখ্যা। যার ফলে কোনও কোনও জায়গাতে বা বলা ভালো যেখানে বিরোধীদের সংগঠন থেকে জনসমর্থন অনেক অনেক বেশি, সেখানে ২০০টার মধ্যে ১৭০ থেকে ১৮০টা আসন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাওয়ার কথা, সেখানে তারা হয়তো ১৩০ থেকে ১৪০টা আসন পাচ্ছে। বিহারে সমর্থন, সংগঠন সবটাই প্রায় সমান সমান ছিল। কাজেই ভোট চুরি দিয়ে সেটাকে প্রায় অয়ান সাইডেড করে তোলা গিয়েছে।
ধ্রুব রাঠি ভিডিও করার অনেক আগেই আমরা বলেছিলাম – (১) শেষ মূহুর্তে নির্বাচন চলাকালীন সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে যে ১০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে, জিতে আসলে আরও দু’লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেটা বিরাট কাজ করেছে। সেই প্রায় দেড় কোটি ‘জীবিকা দিদি’দের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করিয়ে নির্বাচন কমিশনার বিজেপির হয়ে নয়, বিজেপি হয়েই কাজ করেছেন। গোটা নির্বাচনকে এক্কেবারে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট। (২) ডুপ্লিকেট ভোটার যে ছিল, তা তো সেদিনের সেই তাদেরই পোস্ট চেক করে অল্ট নিউজের জুবেইদ জানিয়েছিলেন, রাহুল গান্ধীও এই ডুপ্লিকেট ভোটের কথা বলেছেন। (৩) তাদের ট্রেনে করে হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে আনা হয়েছিল। এটাও নতুন কিছু নয়, কপিল সিব্বল জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও সেই ছবি ছিল। এবং সেটা যে করা যায় না তা নিয়েও পরিস্কার আইন আছে। (৪) সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে বিতর্ক তো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। সরকার আজ নয়, সেই কবেই এই সংক্রান্ত আইন বদলে দিয়েছে। কাজেই সিসিটিভি ফুটেজ থেকে কীভাবে ভোট পড়েছে, কত মানুষকে বাইরে থেকে এনে ভোট দেওয়া হয়েছে, তা বার করা অসম্ভব। (৫) বিহারে এসআইআর চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলোতেও খুব পরিস্কার করে নাম কাটা হবে, বিরোধীদের এলাকা ধরে ধরে নাম কাটা হচ্ছে, এসব কথা তো বলা হয়েছিল। সেটাও নতুন কিছু নয়।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | অমিতাভ বচ্চন থেকে শিল্পা শেঠি, মোদিজির ভয়ে মুখে তালা মেরে বসে আছেন
ভারতীয় সংবিধানের নির্মাতারা এক দূরদর্শী চিন্তাভাবনা থেকে নির্বাচন কমিশনকে এক অসাধারণ ক্ষমতা, ‘এক্সট্রা অর্ডিনারি পাওয়ার’ আর অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, দেশের সমস্ত নির্বাচন – রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা পর্যন্ত – পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একটা এমন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যা যে কোনও রাজনৈতিক চাপের ঊর্ধ্বে থেকে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ আর নিরপেক্ষ রাখতে পারবে। এই প্রতিষ্ঠানকে গণতন্ত্রের প্রহরী বা ‘ওয়াচ-ডগ’ হিসেবে কল্পনা করেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের বাস্তবতা সেই সাংবিধানিক আদর্শ থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছে, তা আজ পরিস্কার। আজ নির্বাচন কমিশন হয়ে উঠেছে এক যন্ত্র, যা দিয়ে নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়। তার শুরুয়াত ২০২৩ সালে। ওই বছরে কেন্দ্র সরকার এক নতুন আইন আনে, যার ফলে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটাই পুরোটা বদলে যায়। আগে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের ভিত্তিতে এক বাছাই কমিটি তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল, যেখানে ভারতের প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা থাকবেন, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এক ধরণের ভারসাম্য রক্ষা করত। কিন্তু নতুন আইনে প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে কমিটিতে নেওয়া করা হয়। এর ফলে, তিন সদস্যের কমিটিতে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (২-১) নিশ্চিত হয়ে যায়। মানে সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন, আর তার পরে তো কেবল হুকুম জারি করার পালা। এটা একটা কাঠামোগত পরিবর্তন, যা নির্বাচন কমিশনকে এক কাঠপুতুল তৈরি করার সুযোগ করে দিয়েছে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়া সমস্ত দেশগুলোতে এটা এক অত্যন্ত পরিচিত কৌশল: যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, আপনাকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে, সেগুলোর দখল নাও। যখন দেশের নাগরিক আর বিরোধী দলগুলো নির্বাচনী রেফারির উপরেই আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় নয়, এটা পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করে। যখন প্রহরী নিজেই ক্ষমতার হাতের পুতুল হয়ে যায়, তখন গণতন্ত্রের দুর্গ বিপন্ন হয়ে পড়ে। আজ ভারতে সেই বিপন্নতা ক্রমশই এক বিরাট চেহারা নিচ্ছে।
আচ্ছা ভারতের গণতন্ত্রের এই হাল নিয়ে যে উদ্বেগ দেশের ভেতরে তৈরি হয়েছে, তা কি কেবল বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক অভিযোগ, নাকি এর কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে? তাহলে আসুন তাকাই কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টের দিকে, যারা বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে। সুইডেনের গোথেনবার্গ-ভিত্তিক ভি-ডেম ইনস্টিটিউট (V-Dem Institute) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউস (Freedom House) – এই দুটো সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের অন্যতম নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য হয়। আর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, এই দুটো রিপোর্টই ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে এক উদ্বেগজনক ছবি তুলে ধরেছে। ভি-ডেমের রিপোর্ট ৪,২০০ জন বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি এবং এতে ১৭৮৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২০২ খানা দেশের প্রায় ৩১ মিলিয়ন ডেটাসেট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুতর। ভি-ডেম ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত ২০১৮ সাল থেকেই আর এক পূর্ণাঙ্গ ‘নির্বাচনী গণতন্ত্র’ নয়। তাদের শ্রেণিবিন্যাসে ভারতকে এক ‘নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র’ (Electoral Autocracy) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল, ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্বাধীনতা – যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন গণমাধ্যম, এবং একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা – এতটাই সংকুচিত হয়েছে যে, নির্বাচনগুলি আর পুরোপুরি অর্থবহ থাকছে না। ভারতে আজ যে সংকট সবচেয়ে গভীর, তা কোনও সাম্প্রদায়িক পরিচিতির সংকট নয়, বরং তা হল ভারতের প্রজাতন্ত্রের আত্মার সংকট। বেঙ্গালুরুর এক বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট কারচুপির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, বিহারে লক্ষ লক্ষ নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার পদ্ধতিগত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা, গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে পরিচিত নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির লাগাতার পতন – এগুলো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলো এক বৃহত্তর এবং পরস্পর সংযুক্ত রোগের উপসর্গ, যা ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোকে ভেতর থেকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তো কোনও এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এটা এক নিরন্তর সংগ্রামের ফল। এই সংগ্রাম চলছে সরকার প্রশাসনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা এবং বিচারব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজের গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের মধ্যে। এই লড়াই চলছে তথ্যের অস্বচ্ছতা এবং তথ্যের অধিকারের মধ্যে। বিপদের ঘণ্টা বাজছে, এবং সেই ঘণ্টা শুনে দেশের নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা জেগে উঠবে, জেগে উঠে কীভাবে সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য কতটা লড়বে? তার ওপরেই নির্ভর করছে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।
লড়াইটা কঠিন, কিন্তু না, এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আর তার শুরুয়াত হতেই পারে এই বাংলা থেকে। হ্যাঁ, এই বাংলা থেকে। কে করবে? তৃণমূল? সিপিএম? বামেরা? সিভিল সোসাইটি? বা সবাই মিলে? নাকি যে যার মতো? যেভাবেই হোক, সবাই রাস্তায় নামলে বাংলায় এই চুরি করা অসম্ভব। আসুন আবার সেই পাঁচটা পয়েন্টে ফেরত যাই। (১) ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভোটের আগে টাকা বিলানো। সম্ভব নাকি এই বাংলায়? বিজেপি করার আগে তো সেই কাজ হাতে নেবে রাজ্যের সরকারে থাকা তৃণমূল দল। আর বিহারের পরে বিজেপি বা নির্বাচন কমিশন কোন মুখে তাকে আটকাবে বা বিরোধিতা করবে? (২) ডুপ্লিকেট ভোটার। গোটা রাজ্যে ১০ থেকে ১৫ হাজারের বেশি এমন ভোটার থাকবে না, থাকা সম্ভব নয়। কারণ বিজেপির না থাকলে, তৃণমূলের, এখনও কিছুটা হলেও বামেদের মাটিতে সংগঠন আছে। এখানে ওটা সম্ভব নয়। (৩) ট্রেনে করে, বাসে করে আনা এই বাংলাতে সম্ভব নয়। কারণ প্রশাসন তৃণমূলের হাতে আছে, আটকে যাবে। (৪) নাম বাদ দেওয়া আরও অসম্ভব। চেষ্টা চরিত্র করলেও হাজার খানেক নামও বাদ দেওয়া যাবে না। (৫) সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে গন্ডোগোল হবে, সেখানেই স্থানীয় প্রশাসন যাবে, তাদের উপরে প্রথম আর কড়া নির্দেশের আগে সিসিটিভি ফুটেজ হাতে নেওয়ার, সরকারের নির্দেশ থাকলে সেটা সম্ভব। এবং তখন সামলানো যাবে না। না বাংলা বিহার নয়, এখানের মাটি আলাদা, মানুষও আলাদা, এখানে নির্বাচন কমিশনের নানান তিকড়মবাজি আমরা দেখেছি। না বাম আমলে না তৃণমূল আমলে, তাদের সেই কায়দাবাজি কাজে দেয়নি।
দেখুন ভিডিও: