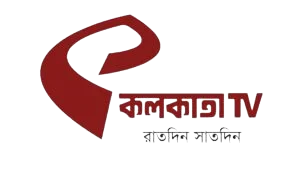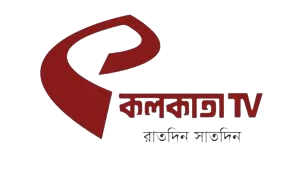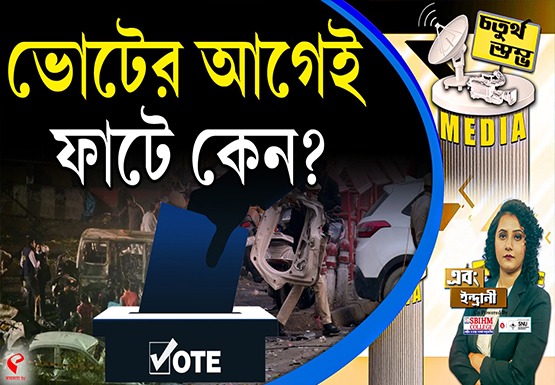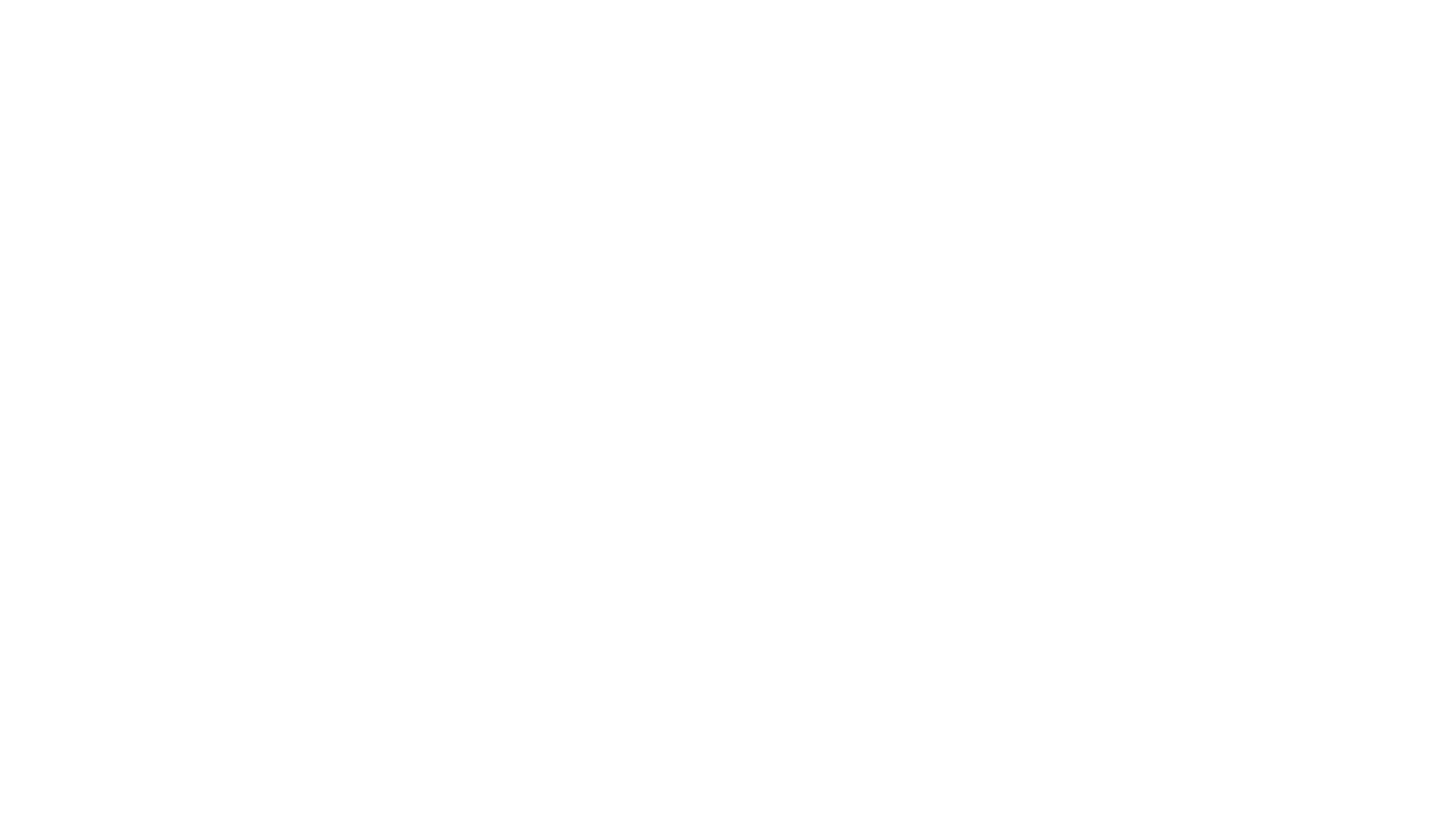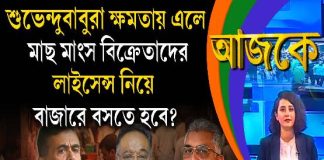ভারতের গণতন্ত্রে ভোট শুধু ঐ প্রতীক বা নীতির উপর ভিত্তি করে তো হয় না; তা প্রায়শই বিরাট এক আবেগের স্রোতে ভাসতে থাকে। কখনও পরিচিতি, কখনও ভাষা, কখনও এক স্লোগান, কখনও বিস্ফোরণ, মৃত্যু আর হত্যা, সেই আবেগ তৈরি করে। যখনই কোনও নির্বাচন ঘনিয়ে আসে, তখন যদি জাতির নিরাপত্তা বা সংহতিকে নাড়িয়ে দেয় বা দিতে পারে এমন কোনও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। তখন সেই আবেগই নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণের অন্যতম ইস্যু হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হল, কেন এই ধরনের ট্র্যাজেডিগুলি, সে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডই হোক বা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, নির্বাচনের ঠিক আগে বা মাঝে সংঘটিত হয়? এটা কি কেবলই কাকতালীয়, নাকি আবেগ নিয়ন্ত্রণের এক সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল? আসুন সেটা নিয়েই কিছু কথা বলা যাক, ভোটের আগেই ফাটে কেন?
মাত্র গতকাল রেড ফোর্ট কার ব্লাস্টের ঘটনাটা এই আলোচনার সুত্রপাত। এখান থেকেই শুরু করা যাক। মঙ্গলবার বিহারে নির্বাচন, এক্কেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, তার আগের সন্ধ্যেতে বিস্ফোরণ মৃত্যু এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দিল্লির মতো এক হাই-সিকিউরিটি জোনে, রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে, সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে ঘটনাটা ঘটছে, মানে এক্কেবারে ‘হার্ট অফ দিল্লি’তে। একটা ধীরগতিতে চলমান গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল, অন্তত ন’জন নিহত, আরও অনেকে আহত। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দেশের রাজধানীতে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা নজরদারি সবচেয়ে বেশি থাকার কথা, সেখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল। বিস্ফোরণটা এতটা শক্তিশালী ছিল যে, এটা কাছের শিসগঞ্জ গুরুদ্বারের ৫০০ মিটার দূরের বাড়ির জানলার কাঁচও ভেঙে দিয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হল, এই বিস্ফোরণের সময় এবং এর সঙ্গে পুলওয়ামার যোগসূত্র। যখন দেশে এক বড় নির্বাচনের শেষ দফার ভোট হবে, তার আগের দিন এই ঘটনা ঘটল। জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণ হওয়া ঐ সাদা হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটা পুলওয়ামার এক বাসিন্দার কাছ থেকেই কেনা হয়েছিল এবং ঘটনার আগে গাড়িটা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পার্কিং লটে ছিল। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনার সঙ্গে ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার একটা বিপজ্জনক মিল খুঁজে পাচ্ছেন, যেখানে বিস্ফোরক বোঝাই একটা গাড়িকে আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও পুলওয়ামার হামলায় মারুতি ইকো ব্যবহার করা হয়েছিল এবং রেড ফোর্ট বিস্ফোরণে হুন্ডাই আই-২০ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু দুটোতেই বিস্ফোরকভর্তি চলন্ত বা ধীরগতিতে চলমান গাড়ির ব্যবহার একই ধরনের সন্ত্রাসী কৌশলের দিকে আঙুল তোলে। এতগুলো কোইনসিডেন্স! কাজেই প্রশ্ন তো উঠবেই যে, এই বিস্ফোরণ কি কেবলই আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, নাকি সুসংগঠিত সন্ত্রাসের কৌশল, যা নির্বাচনী আবেগকে প্রভাবিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে? দিল্লিতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দ্রুত পদক্ষেপ নিলেও, হাই-সিকিউরিটি জোনে এই দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সন্ত্রাস দমনে নজরদারির ক্ষেত্রে কোথাও বড়সড় গলদ রয়ে গিয়েছে, বা গলদ জেনে বুঝেই রাখা হচ্ছে।
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ধরনের ট্র্যাজেডি দু’ভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করেছে: হয় শোকের মাধ্যমে সহানুভূতি আদায় করে, অথবা এক ধরণের রাগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে জাগিয়ে তুলে। এই দু’টো উপায়ই রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে থাকে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে দু’টো প্রধান রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি ভারতের নির্বাচনী মানচিত্রকে আমূল পরিবর্তন করেছিল: ইন্দিরা গান্ধী (১৯৮৪) এবং রাজীব গান্ধী (১৯৯১)-র হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনাগুলো ছিল মূলত ‘সহানুভূতি তরঙ্গে’র জন্মদাতা, যা ছিল জনগণের চরম শোক এবং চরম অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। ইন্দিরা হত্যাকাণ্ডের কয়েক সপ্তাহ পরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে দেশে চরম অস্থিরতার মধ্যে ভোটাররা স্থিতিশীলতার খোঁজেই ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (ইন্দিরা)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েন। এটা ছিল ‘শোকের রাজনীতি’র এক শক্তিশালী উদাহরণ। ভারতীয় ভোটাররা ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে জাতিগত ট্র্যাজেডি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, আর জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কংগ্রেসকে অভূতপূর্ব সমর্থন জানান। ফলস্বরূপ, কংগ্রেস ইতিহাসে সর্বকালের বৃহত্তম নির্বাচনী জয়, ৫৪২টির মধ্যে ৪১১ আসন পেয়েছিল। রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক মাঝে, যখন তিনি তামিলনাড়ুতে প্রচার চালাচ্ছিলেন। প্রথম দফার ভোটের পর কংগ্রেসের পক্ষে পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূল ছিল না। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পর নির্বাচনের বাকি অংশ স্থগিত হয়ে যায় এবং যখন দ্বিতীয় দফার ভোট হয়, তখন দেশজুড়ে আবার এক সহানুভূতির তরঙ্গ তৈরি হয়। ভোটারদের মধ্যে এই ধারণা গেঁথে যায় যে, বিরোধী দলগুলির অস্থির রাজনীতিই হয়তো এই হত্যাকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করেছে। জনগণের তীব্র শোক এবং নেতৃত্ব হারানোর ভয় কংগ্রেসকে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। যদিও কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বড় দল হিসেবে সরকার গঠন করতে পেরেছিল। মানে খুব পরিস্কার যে, যখন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত আসে আর নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি হয়, তখন ভারতীয় ভোটাররা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা দূর করতে পরিচিত এবং ‘নিরাপদ’ নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | প্রচার শেষ, আগামীকাল ভোট, এখনও এক্স ফ্যাক্টর সেই প্রশান্ত কিশোর, পিকে
আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের অংশগ্রহণ কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ইন্দিরা বা রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ডগুলো গণ-সংহতি আর হাই-ডেসিবেল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্ম দিয়েছে, যা স্থিতিশীলতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। আর এই সহানুভূতি আবেগ বা তরঙ্গের উল্টোদিকে, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলা এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এক নতুন ধরনের ‘জাতীয়তাবাদী তরঙ্গ’ ন্যাশনালিস্ট ওয়েভ তৈরি করেছিল, যা ছিল রাগ এবং প্রতিশোধের এক ঝাঁজালো ককটেল। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার নানান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। নোটবন্দী, তাড়াহুড়ো করে জিএসটি চাপানো, আর ক্রমশ বাড়তে থাকা বেকারত্বের কারণে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জন-অসন্তোষ ছিল। বিরোধী দলগুলো যখন এই অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচারকে তুঙ্গে তুলেছিল, ঠিক তখনই ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (CRPF) কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা হয়, যাতে ৪০ জন জওয়ান নিহত হন। বিজেপি দল আর সরকার তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক দুর্বলতার প্রশ্ন থেকে নির্বাচনী ফোকাসকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবাদী গর্বের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আক্রমণের ১২ দিন পর ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বালাকোটে জইশ-ই-মুহাম্মদের (JeM) ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালায়। এটা ছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ভারতীয় বিমান বাহিনীর দ্বারা পাকিস্তানি ভূমিতে প্রথম স্ট্রাইক। এইসব ঘটনা এক ন্যাশনালিস্ট ওয়েভ তৈরি করেছিল, যার ওপরে ভর করে আবার ক্ষমতায় ফিরেছিল বিজেপি। সরকার আর গোদি মিডিয়াগুলো পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদকে চাষ হয়, প্রতিশোধ চাই ইত্যাদি প্রচার শুরু করে, প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রতিটা জনসভায় এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, “আমিই চওকিদার”। মানুষ সেই আবেগে ভাসতে থাকে। মোদিজি নিজেকে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুই হুমকি থেকেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরেন। আর এই ‘চৌকিদার’ ন্যারেটিভ সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ছড়ানো হল, যা হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামরিক পদক্ষেপের অপূর্ব ফিউশন ঘটিয়ে ভোটারদের মূল সমস্যাগুলোর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য করল। ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা তখন গৌণ, তাদের কাছে জাতীয় সুরক্ষা, সামরিক দৃঢ়তা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধই এক নম্বর ইস্যু হয়ে উঠল। যে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কথা, বিজেপি সেই ২০১৯ সালের নির্বাচনে ৩০৩ খানা আসন নিয়ে জিতে ফিরল।
১৯৯১ এবং ১৯৮৪ সালের ঘটনাগুলো সহানুভূতির তরঙ্গ তৈরি করেছিল, এবং ২০১৯ সালের পুলওয়ামা ঘটনা এক মিথ্যে জাতীয়তাবাদী ক্রোধের তরঙ্গ তৈরি করেছিল। কিন্তু রেড ফোর্ট বিস্ফোরণ এক আলাদা ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যা স্বাভাবিক। দিল্লির অন্যতম একট হাই-সিকিউরিটি জোনে কীভাবে বিস্ফোরক বোঝাই এক গাড়ি, যা নাকি আবার পুলওয়ামারই এক বাসিন্দা কিনেছিল, তা দিনের আলোয় অবাধে ঢুকে পড়ল? তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পার্কিং এ থাকল? তারপর কীভাবে সেই গাড়িতেই সন্ধ্যায় বিস্ফোরণ হল? এটা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রাথমিক তদন্তে এক ‘উমর’ নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কথা উঠে আসে, যিনি ফরিদাবাদের এক বিস্ফোরক মামলায় পলাতক ছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, কেবল পাক সাহায্য নয়, সেখান থেকে আসা উগ্রপন্থী নয়, অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদীদের নেটওয়ার্কও রাজধানীতে সক্রিয় এবং তারা খুব সহজে সিকিউরিটি ব্যরিয়ার ভেঙে এ ধরণের ঘটনা ঘটাতে পারছে। যদি সত্যিই এই ঘটনার সঙ্গে পুলওয়ামার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র থাকে, তবে এই বিস্ফোরণ প্রশ্ন তুলবেই—পুলওয়ামার ঘটনা থেকে সরকার কি আদৌ কোনও শিক্ষা নিয়েছে? এসবের বদলে সরকার, স্বরাষ্ট্র দফতর ব্যস্ত নাগরিকত্ব নীতি (CAA) আর নাগরিক পঞ্জি (NRC) নিয়ে। যদিও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (CAPF, BSF) জন্য বিশাল বাজেট বরাদ্দ আছে, অবশ্য এই বরাদ্দ প্রায়শই সীমান্ত সুরক্ষা আর ভিআইপি নিরাপত্তার মতো কাজে লাগানো হয়। আসলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন পরিচিতি-ভিত্তিক রাজনীতি আর ধর্মীয় মেরুকরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে, তখন গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ এবং হাই-সিকিউরিটি জোনের মতো মৌলিক সুরক্ষা প্রোটোকলগুলো অবহেলিতই হতে বাধ্য। এই প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ফোকাস-না থাকাটাই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের সুযোগ করে দেয় আর রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের মতো ঘটনা সেই উপেক্ষারই চরম মূল্য।
“ভোটের আগে ফাটে কেন?” এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর লুকিয়ে আছে ‘আখ্যান নিয়ন্ত্রণ’ বা Narrative Control-এর মধ্যে। মানে সেই ঘটনা কে কারা, কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে? একটা ঘটনা ঘটে গেল, তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে? নাকি ঘটনা ঘটানোর পরে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে? সেটাই মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। (১) যদি ট্র্যাজেডিটা ব্যক্তিগত আর মর্মান্তিক হয় (যেমন, ১৯৮৪, ১৯৯১), তাহলে ক্ষমতাসীন দল স্থিতিশীলতা আর পারিবারিক ধারাবাহিকতার আশ্বাস দিয়ে সহানুভূতি পেতেই পারে। (২) যদি ট্র্যাজেডিটা জাতীয় নিরাপত্তা বা সামরিক বাহিনীর উপর আঘাত হয় যেমন, ২০১৯, তাহলে ক্ষমতাসীন দল দ্রুত, এক প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারে, যা এক ধরণের সিউডো ন্যাশনালিজমের জন্ম দেয়, যা শাসকদলকে ভোটে জিততে সাহায্য করে। কিন্তু রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের মতো ঘটনা, যা নির্বাচনের ঠিক আগে ঘটেছে এবং যেখানে হাই-সিকিউরিটি জোন লঙ্ঘনের ফলে নিরাপত্তা ব্যর্থতা স্পষ্ট, সেখানে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে জাতীয়তাবাদী ক্রোধকে সহজে কাজে লাগানো কঠিন। কারণ, আক্রমণটা ঘটেছে তাদের প্রহরায়, তাদের জামানায়, তাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দেখরেখে। এক্ষেত্রে যদি সরকার ঘটনাটাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে প্রমাণ করতে না পারে এবং পুলওয়ামার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিতই হয়, তবে ভোটারদের মনে নিরাপত্তার ব্যর্থতা এবং সরকারের অগ্রাধিকারের ভুল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতা জনসমর্থনকে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধেও নিয়ে যেতে পারে।
দেখুন ভিডিও: