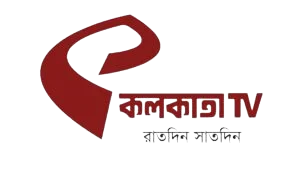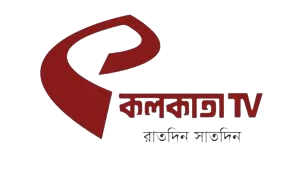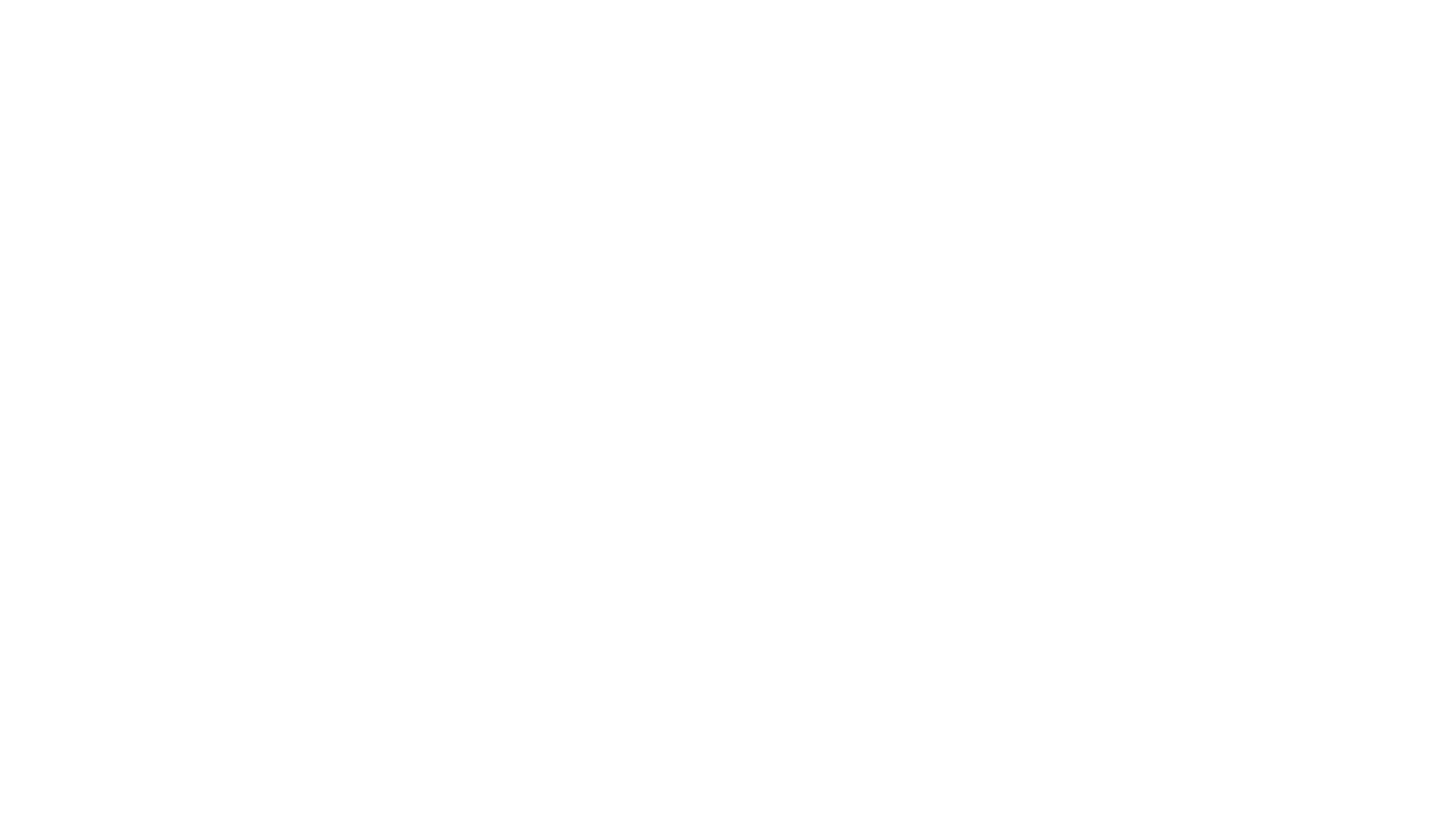মোদিজির দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস ছিল রাম মন্দিরের উদ্বোধন আর ট্রাম্প সাহেবের লিবারেশন ডে ২ রা এপ্রিল, ২০২৫। আগামীকাল ট্রাম্প সাহেব চালু করে দেবেন তাঁর শুল্ক সংক্রান্ত ঘোষণা, সেই কথা আবার জানিয়েছেন। সাফ বলে দিয়েছেন যে আগামীকাল থেকেই ভারতের সমস্ত রফতানি পণ্যে শুল্ক ১০০% বাড়বে। মানে যা ভারত চার্জ করবে, উনিও তাই চার্জ করবেন। অন্য দেশ জানিয়েছে, তারাও শুল্ক বাড়াবে। ভারতের বাণিজ্য দফতর বিভিন্ন সার্কুলারে জানাচ্ছেন কোন প্রডাক্টে শুল্ক কতটা কমানো হল এবং এত করেও কোনও লাভ নেই বোঝাই যাচ্ছে। কারণ শেয়ার বাজার হু হু করে নামছে, এবার সম্ভবত এক ঐতিহাসিক নিচুতে ‘হিস্টোরিক্যাল লো’তে নেমে যাবে। আর মোদিজি চুপ করে বসে হাত কচলাচ্ছেন। আসলে ট্রাম্প আর মোদি—এই দুজনের নাম শুনলেই মনে হয়, এরা যেন সে কবে একই মেলায় হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই, যারা বছরের পর বছর পর আলাদা থাকার পরে একে অন্যকে খুঁজে পেয়েছে। আবার দেখা হয়ে গেছে দুজনার! দুজনেই বড় বড় কথার মালিক, দুজনেই জঙ্গি জাতীয়তাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান, দুজনেই ধুমধাড়াক্কা সিদ্ধান্ত নেন, আর দুজনেই দক্ষিণপন্থী ভাবনার পাক্কা সমর্থক। এদের মিল দেখলে বলতে ইচ্ছে করে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন বা হবুচন্দ্র রাজা-গবুচন্দ্র মন্ত্রী। আসুন এদের মিলগুলো দেখা যাক।
প্রথম মিলটা হল এদের কথা বলার ধরণে—মনে হয় দুজনেই একই স্কুলে বক্তৃতা শিখেছে! ট্রাম্প যেমন “মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন” বলে গলা ফাটান, মোদিও “আচ্ছে দিন আনেওয়ালা হ্যায়” বলে ভোটের মঞ্চ মাতিয়ে দেন। দু’জনেরই কথায় একটা জাদু আছে—হ্যাঁ ম্যাজিক আছে। শুনলে মনে হয়, এই তো, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে! কিন্তু বাস্তবে কী হয়? ট্রাম্পের আমেরিকা আর মোদির ভারত—দু’টো জায়গাতেই লোকে বলে, “ভাই, এই গ্রেটনেস আর আচ্ছে দিন কবে আসবে, একটু ডেটটা বলে দাও!” সে দিন আর আসে না, এঁরা তখন নতুন কিছু নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন।
তারপর চলুন জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে। ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ আর মোদির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’- যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ট্রাম্প বলেন, “বাইরের লোক এসে আমাদের চাকরি খেয়ে নিচ্ছে,” তাই তিনি মেক্সিকোর সীমান্তে দেওয়াল তুলে দিলেন। মোদিও বলেন, “ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় পণ্য,” তাই ‘আত্মনির্ভর ভারত’ নিয়ে এলেন। দু’জনেরই মনে একটাই ভাবনা—আমরা সেরা, বাকিরা পরে আসুক! এই জাতীয়তাবাদের চাকায় এত জোরে হাওয়া দিয়েছেন যে, বাকি বিশ্ব মাঝে মাঝে বলে, “ভাই, একটু ব্রেক কষো, আমরাও তো পৃথিবীতে আছি!” ওনারা চলেন নিজের মনে, বয়েই গেছে বিশ্বের মানুষজনের কথা শুনতে।
এবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরণ। ট্রাম্প যেমন হঠাৎ একদিন ঘোষণা করে দিলেন, “মুসলিম দেশ থেকে কেউ আমেরিকায় ঢুকবে না,” মোদিও এক রাতে বলে দিলেন, “আজ থেকে ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোট চলবে না!” দুজনেরই সিদ্ধান্তে একটা ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার আছে—যেন বলছেন, “দেখো, আমি বড় নেতা, আমি যা বলবো তাই হবে!” কিন্তু এই ধুমধামের পর লোকে যখন লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলতে গেল, বা ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় বিমানবন্দরে আটকে পড়ল, তখন সবাই বলল, “ভাই, এত তাড়ার কী ছিল?” মনে আছে করোনার সময়ে লকডাউনের কথা? ২৪ ঘন্টার নোটিশে লকডাউনের সত্যিই কী দরকার ছিল?
আর দক্ষিণপন্থী ভাবনা? দুজনেই যেন দক্ষিণপন্থীদের পোস্টার বয়! ট্রাম্প সাদা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আর জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, মোদিও হিন্দুত্ব আর জাতীয়তাবাদের পতাকা উড়িয়ে দেন। ট্রাম্প প্যালেস্তাইনি ছাত্রদের পিছনে লাগেন, মোদিও সমস্ত বিরোধী কণ্ঠকে ‘দেশবিরোধী’ বলে চুপ করিয়ে দেন। দু’জনেরই মনে একটা ভাবনা—যারা আমার সঙ্গে একমত নয়, তারা আমার দেশের জন্য ভালো নয়। এই ভাবনায় দুজনেই যেন একই গাছের দুই ডাল!
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদিজির একমাত্র বিকল্প
মজার ব্যাপার, দুজনেরই ফ্যান ফলোয়িং আছে বিস্তর। ট্রাম্পের সমর্থকরা যেমন তার জন্য জান দিতে রাজি, মোদির ভক্তরাও তাকে ‘দেশের ত্রাণকর্তা’ বলে পুজো করে। দু’জনেই জানেন কীভাবে ভিড়কে মাতিয়ে রাখতে হয়—একজন টুপি পরিয়ে, আরেকজন পাগড়ি পরিয়ে! তবে এই দুই ভাইয়ের মিল দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, এরা যদি সত্যিই মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাই হয়, তাহলে মেলার মাইকে ঘোষণা করা উচিত, “ট্রাম্প আর মোদি, তোমাদের একসঙ্গে একটা দল গড়তে হবে—জাতীয়তাবাদী ভাইদের দল!” ট্রাম্প আর মোদি দুজনেই বামপন্থার ভূত দেখেন, মোদিজি আর তাঁর সরকার জেএনইউ-তে ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ দেখতে পান আর ট্রাম্প সাহেব ক্ষ্মতায় এসেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতে সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এনারা দুজনেই ‘বামপন্থী’ গবেষণা বন্ধ করতে চান, যেটা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা। এটা নতুন নয়, কারণ ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবসময় পিছিয়ে থাকা মানুষদের লড়াইয়ের জায়গা ছিল। ট্রাম্পের নির্দেশের ফল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তার সাদা শ্রেষ্ঠত্ব, নারীদের প্রতি বৈষম্য আর জাতীয়তাবাদ পড়াশোনার স্বাধীনতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধ আর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য হুমকি। এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে স্বাধীনতার পরের সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনা করা যায়। তখন আফ্রিকান আর ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্য, জেন্ডার স্টাডিজ, ইকোফেমিনিজম, তৃতীয় বিশ্বের কালচারাল স্টাডিজ আর যুদ্ধবিরোধী সাহিত্য পড়ার চল বেড়েছিল। এই পড়াশোনাগুলো বড় বড় গল্পকে চ্যালেঞ্জ করত, আর অসাম্য আর একনায়কতন্ত্রের বাইনারি সিস্টেম ভাঙার চেষ্টা করত।
ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সির সময় দেখা গিয়েছে, তিনি একতরফা সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছেন, বিশেষ করে ইমিগ্রেশন নীতিতে। তার ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির জন্য কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল—যেমন মুসলিম দেশগুলোর ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আর আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে দেওয়াল তৈরি। আর সম্প্রতি তিনি ফিলিস্তিনের সমর্থকদের পেছনে লেগেছেন। ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নীতি তার জাতীয়তাবাদ আর পপুলিস্ট ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে, যেখানে তিনি আমেরিকার চাকরি আর সংস্কৃতি বাইরের হুমকি থেকে বাঁচাতে চান। অনেকে এটাকে বৈষম্যমূলক আর জেনোফোবিক বলে সমালোচনা করেছে, কেউ কেউ বলছে এটা নাজিবাদের কাছাকাছি। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে বেশ কিছু বিতর্কিত নির্দেশ এসেছে। ২০১৭-তে তিনি একটা নির্দেশে বেশ কিছু মুসলিম দেশ থেকে ইমিগ্রেশন বন্ধ করে দেন। আমেরিকার ৫০-এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট একসঙ্গে চিঠি লিখে বলেন, এটা আমেরিকার বৈচিত্র্য আর সবাইকে গ্রহণ করার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। তারা বলেন, ইমিগ্র্যান্ট ছাত্ররা আমেরিকার প্রযুক্তি, গবেষণা আর শ্রমে অনেক অবদান রেখেছে। কিন্তু ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সিতে আরেকটা নির্দেশে প্যালেস্তাইনের সমর্থকদের টার্গেট করা হল, তখন এত বিরোধিতা দেখা যায়নি। ট্রাম্পের নীতি ক্যাম্পাস আর আন্তর্জাতিক ছাত্রদের উপর বড় প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে যারা অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলে আর বৈচিত্র্যের পক্ষে। প্যালেস্তাইনি ছাত্র আর ট্রাম্পের ইজরায়েল নীতির বিরোধী কণ্ঠগুলোর ওপর হামলা হয়েছে, যার ফলে ক্যাম্পাসে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেক ছাত্র আর শিক্ষক কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কারণ তারা শাস্তি পেতে পারে।
এটা চিন্তার, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তো বৈচিত্র্য, সবাইকে নেওয়া আর মুক্ত কথা বলার জায়গা হওয়া উচিত, গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য শাস্তি দেওয়ার জায়গা নয়। মজার ব্যাপার, আমেরিকা তো ইমিগ্র্যান্টদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিকভাবে অনেক লাভ করেছে! ট্রাম্পের ভাবনার জন্য প্যালেস্তাইন-বিরোধী মনোভাব বেড়েছে। কিছু রাজনীতিবিদ বলছে, প্যালেস্তাইনের পক্ষে বিক্ষোভ করা বিদেশি ছাত্রদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত। এতে ক্যাম্পাসে ভয় আর হুমকির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেক ছাত্র আর শিক্ষক অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কারণ তারা হয়রানি বা দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ভয় পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য এটা আরও বড় সমস্যা, কারণ তাদের ভিসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা অন্য শাস্তি পেতে পারে। ক্যাম্পাসে বিরোধী কণ্ঠ বন্ধ করার এই প্রভাব গণতন্ত্র, মুক্ত কথা আর মানবাধিকারের জন্য বড় হুমকি। এটা কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটা বিরাট গল্পের ছোট্ট অংশ, ট্রাম্পের ইমিগ্র্যান্ট-বিরোধী কথাবার্তা শুধু একটা দোষী খোঁজার জন্য নয়। এটা এক জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আর অন্ধ দেশপ্রেমের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চায়, আর তা সর্বাত্মকভাবেই গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে। তিনি অবাধ ইমিগ্রেশনের বিরোধী, কারণ তিনি মনে করেন এতে আমেরিকান শ্রমিকদের চাকরি চলে যাচ্ছে। এই ভাবনা ইউরোপ আর অন্য জায়গায় দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একইভাবে মোদিজি সিএএ পাশ করিয়ে, এনআরসি চালু করে ঠিক সেই কাজটাই করতে চান। দুই শাসনেই সংখ্যালঘুরা ভয় পাচ্ছেন, গণতান্ত্রিক মানুষজন কুঁকড়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুব জরুরি। ট্রাম্পের এই নেতৃত্ব, মোদিজির এই নেতৃত্ব যা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় না আর স্বার্থপর কিছু এজেন্ডা নিয়েই চলে, তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ আর চিন্তাবিদদের জনমত তৈরি করতে হবে, বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, আর প্রগতিশীল মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলতে হবে। মোদি-ট্রাম্পের এই বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আশ্রয়স্থল হতে হবে, যেখানে বিরোধী কণ্ঠ আর সমালোচনামূলক চিন্তা ফুটে উঠবে। মোদি-ট্রাম্পের এজেন্ডা, যেটা র্যাডিকাল গবেষণা আর মানসিকভাবে চাপে থাকা ছাত্রদের দমিয়ে দেয়, এটা এক ধরনের একনায়কতন্ত্র। এর প্রভাব শুধু ভারতবর্ষ বা আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, আর এটা বিশ্বব্যবস্থা আর মানবাধিকারের জন্য হুমকি।
তবে একটা ব্যাপারে এই দু’জনে এক্কেবারে আলাদা, ট্রাম্প সাহেব দিনের শেষে আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করার কথা ভাববেন না, ওনার লক্ষ্য আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধি, কিন্তু মোদিজির লক্ষ্য দেশের কিছু শিল্পপতির সম্পদ বৃদ্ধি আর তাকে সুরক্ষিত রাখা। তা না হলে সারা পৃথিবীর দেশগুলো যখন ট্রাম্পের এই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তখন মোদিজির গলায় একটাও কথা নেই, দুষ্টু মানুষেরা বলছেন আদানির মামলাটা সামনে রেখেই মোদিজি একটা ডিল করে নিতে চান, সত্যি মিথ্যে জানিনা, তবে ঘটনা হল ট্রাম্প সাহেব আদানির মামলা আপাতত হলেও আটকে দিয়েছেন। হ্যাঁ দেশের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে এই ফারাক ছাড়া ট্রাম্প আর মোদিজি ঐ মেলায় হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই বললে খুব অন্যায় কিছু বলা হবে না।