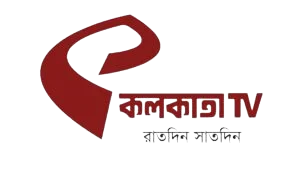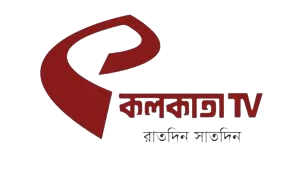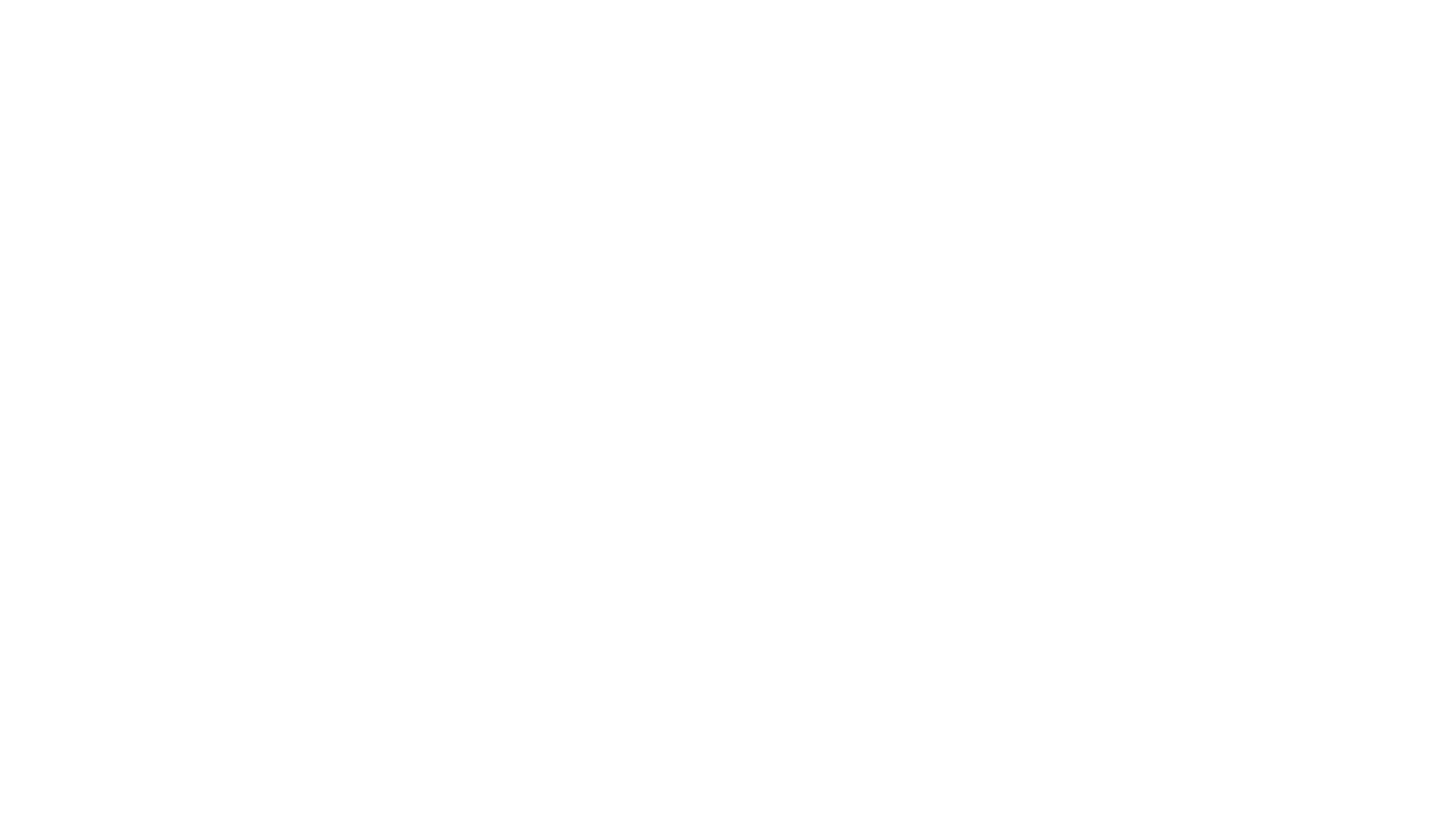লাদাখে আগুন, রাস্তায় জেন জি-র মিছিল, সমস্ত রাজনৈতিক দল বাদ দিয়ে বিজেপির দফতর পোড়ানো হল, সরকারি কিছু দফতরেও ভাঙচুর দেখলাম আমরা। আর তারপর থেকে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভারতেও? ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ ও রাজ্য ভাগের পর আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পেয়েছিল লাদাখ। কিন্তু সেখানে সেই সময় থেকেই পূর্ণ রাজ্যের দাবি তীব্র হচ্ছে। কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চললেও তা সন্তোষজনক হয়নি। ১৪ দিন ধরে এই দাবিগুলির সমর্থনে অনশন করছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ও তাঁর কয়েক জন সঙ্গী। এটাই প্রথম নয়, বেশ কয়েকবার তিনি অনশনে বসেছেন, সারা দেশ থেকে সমর্থনও পেয়েছেন। কিন্তু কোথাও কি তাহলে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে? যদি কাশ্মীরের ইতিহাস দেখেন তাহলে দেখবেন কাশ্মীর ভ্যালি বা জম্মুতে বারবার নানান ইস্যুতে আগুন জ্বলেছে। সংঘর্ষ, মৃত্যু সেখানে নতুন কথা নয়। কিন্তু লাদাখ সেই আগুন বৃত্তে ছিল না কোনওদিন। যাঁরা লাদাখ গিয়েছেন তাঁরা জানেন, ‘সাত চড়ে রা নেই’ বলতে যা বোঝায়, সেটাই হলেন এই লাদাখের মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে এক দীর্ঘ টানা লড়াই তাঁদের সর্বংসহা করে তুলেছে। সেই লদাখেও আগুন জ্বলছে, সেটা খবর বৈকি! আর ঠিক এটাই হল বিজেপির অবদান। ফ্রিঞ্জ এলাকাগুলোতে যেখানে তাঁরা ঢূকতে পারেন না, পারছেন না, সেখানে আগুন লাগছে, কিন্তু থামছে না। মণিপুরের পরে লাদাখ হল সেই জায়গা। মিলিয়ে নেবেন, বিজেপি এই অশান্তি জিইয়ে রাখবে। সংবিধান বিরোধী কোনও দাবি নয়, পূর্ণ রাজ্যের দাবি। সেই সঙ্গে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত করা-সহ আরও বেশ কয়েকটা প্রত্যাশা।
এই তো, এবং সেই লড়াই ও আজ নয় গত দু আড়াই বছর ধরে চালাচ্ছেন ঐ সোনম ওয়াংচুক। তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জমতে থাকা অসন্তোষ অবশেষে লাদাখে রূপ নিল হিংসাত্মক বিক্ষোভের। যার পুরোভাগে রইলেন যুবকেরাই। যাঁরা ‘জেন জি’-র সদস্য বলে দাবি কয়েকটি শিবিরের। হিংসার ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হল। মানুষ যদি দেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে, সাধারণ প্রতিবাদ, ধরণা মিছিলে তাঁর দাবি কানেই নিচ্ছে না সরকার, তখন আন্দোলনের চেহারা পাল্টায়। সেটাও কানে বা মাথায় না ঢুকলে, সামনে আসবেই জেন জি-রা, যাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা লে-তে হয়েছে। কিন্তু সেখানেই শেষ হবে, এরকমটা মনে করার কোনও কারণই নেই। ক’দিন আগেই তো দেখেছিলাম, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, ৭ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রীকে রাস্তায় পকেটমারের মত ফেলে পেটানো হয়েছিল। কেপি শর্মা ওলির বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল, মন্ত্রীদের বাড়ি, নেপালি কংগ্রেসের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। এমনকি মাওবাদি কমিউনিস্ট নেতা প্রচন্ডের বাড়িও বাদ পড়েনি। এই কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন অস্থিরতা চোখে পড়ছে, যা এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। শ্রীলঙ্কায় এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় কীভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত এক পারিবারিক রাজবংশের পতন ঘটিয়েছিল, তার রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলাদেশে এক সীমিত কোটা সংস্কার আন্দোলন কীভাবে এক বিশাল গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়ে সরকার পরিবর্তন ঘটাল, তা আমরা দেখেছি। নেপালে সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিক্ষোভ কীভাবে বেকারত্ব আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নিল। এবার লাদাখে সেই ব্যপকতা না থাকলেও চেহারাটা খুব পরিষ্কার। কাজেই খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন হল, এই গণবিক্ষোভের ঢেউ কি এবার ভারতেও আছড়ে পড়তে পারে, নাকি ভারতের পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা?
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | ধসছে ভারতের শেয়ার বাজার, পড়ছে টাকার দাম, মোদিজি কী করছেন?
(১) শ্রীলঙ্কার বিপর্যয় থেকেই শুরু করা যাক, যেখানে অর্থনীতিই ছিল একমাত্র কারণ। শ্রীলঙ্কার গণবিক্ষোভের মূল চালিকাশক্তি কোনও রাজনৈতিক দল বা নির্দিষ্ট সামাজিক ইস্যু ছিল না; এটা ছিল এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অচল করে দিয়েছিল। এই সংকটের পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। ২০১৯ সালে গোতাবায়া রাজাপাকসে সরকার ক্ষমতায় এসে এক অযৌক্তিক কর ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, যা সরকারের রাজস্ব মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়। এর সঙ্গে যোগ হয় চড়া সুদের বাণিজ্যিক ঋণের ওপর বিরাট নির্ভরতা। বিশ্বব্যাঙ্কের এক প্রতিবেদন বলছে, ২০১৯ সাল নাগাদ শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক ঋণের ৫৬ শতাংশই ছিল এই বাণিজ্যিক ঋণ, যেখানে ২০০৭ সালে এই হার ছিল মাত্র ২.৫ শতাংশ। যখন মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা—যেমন জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস—তীব্র ঘাটতি এবং নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জমা হয়, আগুন লাগে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন, যা প্রায় দেড় দশকের এক পারিবারিক রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটায়। (২) বাংলাদেশের পরিবর্তন, আদতে এক কোটা বাতিলের আন্দোলন সরকার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয়েছিল এক নির্দিষ্ট ও সীমিত দাবিকে কেন্দ্র করে—সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার। কিন্তু আন্দোলন দমনে সরকারের চুড়ান্ত দমনমূলক ব্যবস্থা, পুলিশি জুলুম, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ‘প্রতারণামূলক’ ভাষণ এবং দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। ফলে আন্দোলন দ্রুতই কোটা সংস্কারের সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে ‘বৈষম্যবিরোধী’ এবং ‘অসহযোগ’ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়, যা সাধারণ মানুষকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ৫ অগাস্ট, তৎকালীন সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, সেনাবাহিনী আর জনগণের উপর গুলি চালাতে রাজি নয়। সামরিক বাহিনীর এই নিরপেক্ষ অবস্থানই সরকারের পতনের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে কাজ করে। দুপুর ২টার দিকে যখন সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান, তখন লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং সেদিনই সরকার পতন হয়। বাংলাদেশের ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, একটা সরকার যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে, তবে সেই দমন-পীড়নই জনগণকে আরও বেশি উস্কে দিতে পারে। (৩) নেপালে বিক্ষোভের সরাসরি সূত্রপাত হয়েছিল সরকারের এক আপাতদৃষ্টিতে ছোট সিদ্ধান্তের কারণে—২৬টা সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোও ছিল, সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। সরকার জানিয়েছিল, প্ল্যাটফর্মগুলো সরকারের কাছে রেজিস্টার্ড না হওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যবসা ও পর্যটন মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে এবং প্রবাসে থাকা স্বজনদের সঙ্গে নাগরিকদের যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। লাখ লাখ মানুষ, যারা এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাঁরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বিক্ষোভ এক বিরাট চেহারা নেওয়ার পরে বিক্ষোভকারীরা নিজেরাই বলছে, এটা শুধু একটা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। এই আন্দোলনের মূল কারণ হল নেপালের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে এক তরুণ বলছেন, “নেতাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যদি উজ্জ্বল হয়, তাহলে আমাদেরটা কোথায়?”
দক্ষিণ এশিয়ার এই তিন দেশের ঘটনা প্রবাহ এই প্রশ্ন তো তুলবেই যে ভারতেও কি এই একই রকমের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে? লাদাখের ঘটনা কী সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে? এটা ঘটনা যে, শিক্ষিত অথচ বেকার যুবসমাজ, যাদের উচ্চাশা আছে কিন্তু সুযোগ নেই, তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পারে। আগে যে হয়নি তাও তো নয়! প্রথমত, মোদি সরকারের আনা তিনটে বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকরা দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে দিল্লির সীমান্তে অবস্থান বিক্ষোভ করে। কৃষকদের মূল দাবি ছিল, কর্পোরেট পুঁজির হাত থেকে কৃষিকে বাঁচানো এবং ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) নিশ্চিত করা। সরকার প্রথমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করলেও, আন্দোলনের তীব্রতা ও কৃষকদের সংকল্পের কাছে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং বিতর্কিত তিনটে আইনই প্রত্যাহার করে নেয়। দ্বিতীয়ত, ২০১৯ সালে পাশ হওয়া বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের (CAA) বিরুদ্ধে সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। এই আইন আমাদের দেশে প্রথমবার নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মকে এক মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে, যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের পরিপন্থী। এই আন্দোলন ছিল মূলত আদর্শগত এবং শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে, হায়দ্রাবাদ, দিল্লির শাহিনবাগ, মুম্বই, কলকাতা। সরকারের কঠোর দমন-পীড়ন এও সামলানো যাচ্ছিল না, সরকারের মধ্যে নান্ন প্রশ্নও উঠছিল, কিন্তু মূলত কোভিড-১৯-এর কারণে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই দুটো আন্দোলন দেখায় যে, ভারতীয় সরকার একদিকে যেমন সুসংগঠিত আন্দোলনকে (কৃষক আন্দোলন) চাপের মুখে ছাড় দিতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি দমন-পীড়নের মাধ্যমে আদর্শগত আন্দোলনকে (সিএএ-বিরোধী আন্দোলন) খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। ভারতের মূল সমস্যা হল, এখনও কোনও একক ঘটনা ঘটেনি যা কৃষক আন্দোলন বা সিএএ-বিরোধী আন্দোলনকে দেশের অর্থনৈতিক সংকটগুলোর (বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি) সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথতে পেরেছে।
তাহলে এর পরের প্রশ্ন হল, ভারতের পরিস্থিতি কেন আলাদা? দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোতে সংঘটিত গণবিক্ষোভের মূল কারণ এবং ফলাফলগুলোকে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে কয়েকটা মৌলিক পার্থক্য সামনে আসে। যেমন, শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তীব্র মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি থেকে, যার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, এক সীমিত কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের জন্ম হয়, যার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য ও দুর্নীতি। সরকার প্রথমে দমন-পীড়ন ও ইন্টারনেট বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে সরকারের পতন ঘটে। নেপালের বর্তমান বিক্ষোভের সূত্রপাত হয় সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার কারণে। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে গভীর বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং তরুণ প্রজন্মের হতাশা। অন্যদিকে, ভারতে বিতর্কিত কৃষি আইন বা সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের মতো বড় বিক্ষোভ হলেও, সেগুলো সুনির্দিষ্ট কারণকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। সরকার কৃষক আন্দোলনের মুখে আইন প্রত্যাহার করলেও, সিএএ-বিরোধী আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়, যার ফলে ভারতে আন্দোলনগুলো হয় দমন হয়েছে অথবা সীমিত দাবি আদায় করতে পেরেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক বেশি কৌশলগতভাবে শক্তিশালী। তারা প্রয়োজনে একদিকে কঠোর দমন-পীড়ন চালাতে পারে যেমন সিএএ-বিরোধী আন্দোলন, আবার অন্যদিকে আন্দোলনের তীব্রতা দেখে দাবি মেনে নিতেও দ্বিধা করে না মাথায় রাখুন কৃষক আন্দোলনের কথা। তার উপরে, ভারতে রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো বিভক্ত ও দুর্বল, যা জনগণের ক্ষোভকে এক একক প্ল্যাটফর্মে আনতে ব্যর্থ। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপালের বিক্ষোভগুলো হয় স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন ছিল (শ্রীলঙ্কা, নেপাল) অথবা এক সুসংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল (বাংলাদেশ)। এবং এসবের উপরে রয়েছে ১৯৫০ থেকে লাগাতার নির্বাচন, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হাতবদলের ইতিহাস। মানুষ এখনও মনে করে যে, নির্বাচনের মাধ্যমেই এক সরকার, সে যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন, তাকে বদলানো যায়। ইন্দিরা গান্ধীর মতো স্বৈরাচারী সরকারেরও পতন দেখেছি আমরা। কাজেই এক অটূট বিশ্বাস মানুষের আছে এই দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার উপরে, যা কিন্তু এই দেশগুলোতে ছিল না। রাজতন্ত্র, মিলিটারি রুল ইত্যাদি মিলিয়ে এক বিরাট সময় ধরে মানুষকে সমস্ত ব্যবস্থার উপর থেকে বিশ্বাস তুলে নেওয়ার ইচ্ছেগুলোকে বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতে ১৯৫০ থেকে আজ অবধি সব রাজ্যে বা কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হয়েছে নির্বাচনেই। কিন্তু ঠিক এই মূহুর্তে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস চলে যাচ্ছে, বা সরকার এমন কিছু করছে যাতে করে মানুষ মনে করছে আমার ভোটে কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর তাই এই মুহূর্তে ভারতে এই দেশগুলোর মতো একটি সর্বব্যাপী গণবিস্ফোরণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম হলেও একেবারে নেই, একথা বলা যাবে না। বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে, এবং জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, ইনফ্লেশনের মতো সমস্যাগুলো এক ‘টাইম বোম’-এর মতো কাজ করছে। যদি ভবিষ্যতে সরকার এমন কোনও বিতর্কিত আইন বা নীতি নিয়ে আসে, যা এই গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তা এক নতুন ধরনের এবং সম্ভবত আরও ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। প্রশ্নটা তাই ‘হবে কী না’ নয়, বরং ‘কবে হবে’ এবং ‘কী চেহারাতে হবে’। যেদিন হবে সেদিন জানি আমরা অনেক মূল্য দিতে হবে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়া এই আগুন আমার দেশেও জ্বলবে না, তেমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না।