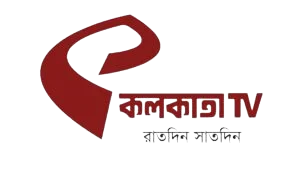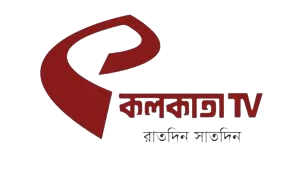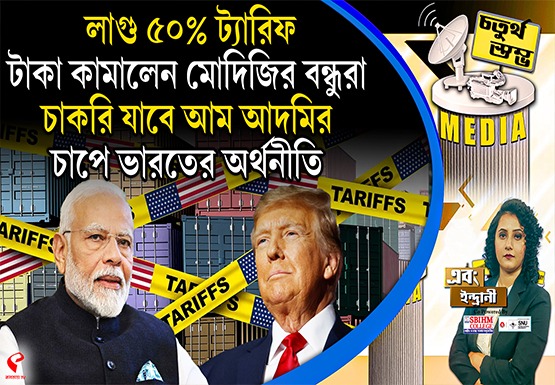মোদিজির ‘মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড’ ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজিকিউটিভ অর্ডার অনুযায়ী, ২৭ তারিখ মাঝরাত থেকেই ৫০ শতাংশ রফতানি শুল্ক বা ট্যারিফ চেপে গেল। কোন কোন শিল্পে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা সাংঘাতিক প্রভাব ফেলবে? মানে চাকরি যাবে, বাণিজ্য কমবে? এমএসএমই, ক্ষুদ্র-মাঝারি-ছোট শিল্প, সেখানে চাকরি যাবে, বহু এমএসএমই-তে লালবাতি জ্বলবে? দদতরের মন্ত্রী কে? জিতন রাম মাঞ্ঝি। তিনি কী করছেন? বিহারে ভোট নিয়ে ব্যস্ত। প্রবল ধাক্কা আসবে ফিশারিজ, এনিম্যাল হাসবান্ড্রি, ডেয়ারি শিল্পক্ষেত্রে। মন্ত্রী কে? রাজীব রঞ্জন সিং। কোথায় তিনি? বিহারে নির্বাচনের জনসভায়, লক্ষ লক্ষ নতুন চাকরির কথা বলছেন। ভয়ঙ্কর ধাক্কা খাবে টেক্সটটাইল, বস্ত্র শিল্প। মন্ত্রী কে? গিরিরাজ কিশোর। তিনি কোথায়? বিহারে, নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। মানে এই যে ৫০ শতাংশ রফতানি শুল্ক, তা এই শিল্পক্ষেত্রগুলোতে কোথাও ৩০, কোথাও ৩৫, কোথাও আবার ৪০ শতাংশ ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু দেখুন সেই দদতরের মন্ত্রীদের হুঁশ নেই। এই বিরাট সংকটের সময়ে সেই মন্ত্রীরা তাঁদের দফতরে বসে এটা ভাবছেন না যে, কী করে এই সংকটের মোকাবিলা করা যায়। ওনাদের আপাতত চিন্তা হল বিহারে যে কোনও মূল্যে গদি বাঁচানো। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী, এক আদ্যন্ত মিথ্যেবাদী প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ভারতে যা তৈরি হচ্ছে, সেটা কিনুন। যে দেশ একটা মোবাইল চিপ তৈরি করে না, একটা ইলেকট্রনিকস গুডসের চিপ তৈরি করে না, টিভির পিকচার টিউব থেকে ল্যাপটপের মাদার বোর্ড আসে বাইরে থেকে, ওষুধের ইনগ্রেডিয়েন্ট আসে বাইরে থেকে, ক্যামেরার লেন্স আসে বাইরে থেকে, বাল্বের কমপোনেন্টস আসে বাইরে থেকে। দেশ হয়ে উঠেছে সস্তায় অ্যাসেম্বলিংয়ের আড়ত, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান দিচ্ছেন ‘বি লোকাল’, সেই তিনি যিনি ফ্রান্সের মঁ ব্লাঁ পেন ব্যবহার করেন, কার্তিয়েরের সান গ্লাস, আর বিলেতে তৈরি রেঞ্জ রোভারে চড়েন, তিনি জ্ঞান দিচ্ছেন ‘বি লোকাল’। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, আমেরিকার উন্মাদ ট্রাম্পের নির্দেশ মতো আমরা চলব নাকি? তিনি বললেই আমাদের সস্তার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে? আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য সস্তার তেল আমরা যেখান থেকে পাব, সেখান থেকেই কিনব। তাতে একদা মোদিজির গলায় গলায় বন্ধু উন্মাদ ট্রাম্প কত শতাংশ ট্যাক্স চাপাবেন, সেটা তো প্রথম বিবেচ্য নয়, দেখতে হবে ভারতের স্বার্থ। এ পর্যন্ত ঠিক আছে, ‘ভাসুর ভাতৃবৌয়ের সম্পর্ক’ তাই ট্রাম্প সাহেবের নাম মুখে না এনেও মোদিজি বলার চেষ্টা করছেন ঠিক এটাই যে, দেশের স্বার্থ, আম আদমির স্বার্থ, কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সবচেয়ে আগে। কিন্তু সত্যিই কি দেশের স্বার্থকে সামনে রেখেই রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করা হয়েছিল? সত্যিই কি রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল আমদানি করে দেশের মানুষের, আম জনতার কোনও লাভ হয়েছিল? আসুন সেই সত্যিটাও বুঝে নিই।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হল, তখন বিশ্বজুড়ে এনার্জি মার্কেটে আগুন লেগে গেল। আর বাজারে আগুন লাগলে হিসেব করে দেখুন, লাভ কামায় ফড়ে দালালেরা। এক্ষেত্রেও আলাদা কিছু হয়নি, বিশেষ করে সেই ফড়েদের পিছনে যখন রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশ ছুঁতে শুরু করল, আর তার আঁচ এসে লাগল ভারত সমেত বিশ্বের প্রায় সব দেশের অর্থনীতিতে। ঠিক সেই টালমাটাল সময়ে মোদিজি জানালেন পশ্চিমের দেশগুলোর চাপ উপেক্ষা করে রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল ছাড়ে অপরিশোধিত তেল কেনা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে দেশের শক্তি সুরক্ষা (Energy Security) নিশ্চিত করার এক যুগান্তকারী ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হিসেবে তুলে ধরা হল। গোদি মিডিয়াতে হৈ হল্লা। দেশপ্রেমী মোদিজি নাকি আমেরিকার কাছ থেকে দামী তেল না কিনে সস্তার তেল কিনতে গেলেন রাশিয়ার কাছে। দেশের মানুষকে বোঝানো হল, এই সিদ্ধান্তের ফলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে না এবং সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে থাকবে। এবং যুক্তি খুব সহজ একটা স্বাধীন দেশ যার কাছ থেকে সস্তায় তেল পাবে তার কাছ থেকেই কিনবে। এতে অন্যায়ের তো কিছু নেই, দেশের মানুষের স্বার্থই প্রথম বিবেচ্য। হ্যাঁ। এরকমটাই বললেন মোদিজি এবং ওনার পিছন থেকে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। ডাহা মিথ্যে বললেন, লোককে ঠকানোর জন্য এসব বললেন। কিন্তু এই গল্পের আড়ালে থাকা আসল সত্যিটা কী? সস্তায় পাওয়া রাশিয়ান তেলের সেই গঙ্গা কি সত্যিই দেশের সাধারণ মানুষের উঠোন পর্যন্ত পৌঁছেছিল? নাকি সেই স্রোত মাঝপথে বাঁক নিয়ে জমা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠীর কোষাগারে?
আসলে রাশিয়ার সস্তা তেলের সিংহভাগ মুনাফা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নায়ার এনার্জির মতো বেসরকারি সংস্থাগুলি করেছে। আর একই সময়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনকারী সংস্থাগুলি লোকসানের পরিমাণ বেড়েছে। এবং সাধারণ মানুষ পেট্রোল-ডিজেলের দামে এর প্রায় কোনও সুফলই পায়নি। বদলে আমেরিকার চাপানো শাস্তিমূলক শুল্কের বোঝা এবার পুরো দেশের অর্থনীতিকে বইতে হচ্ছে। আসলে মোদি সরকারের কাছে আম আদমি নয়, আম্বানি আদানির মুনাফা বাড়ানোটাই হল আসল লক্ষ্য। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ভারতের তেল আমদানিতে রাশিয়ার অংশ প্রায় ছিল না বললেই চলে, মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। কিন্তু ২০২২ সালের পর এই চিত্রটা নাটকীয়ভাবে বদলে গেল। খুব কম সময়ের মধ্যেই রাশিয়া ভারতের বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী দেশে হয়ে উঠল। যার ফলে ঐ ১ থেকে ২ শতাংশ থেকে মোট আমদানি প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ হয়ে গেল। এই তেল কেনা হচ্ছিল আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার পর্যন্ত অবিশ্বাস্য ছাড়ে। এই বিপুল পরিমাণ সস্তা তেল ভারতের বাজারে বন্যার মতো ঢুকে পড়ে, আর এই সুযোগকে কাজে লাগানোর দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল কিন্তু দেশের সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ব নয়, বেসরকারি শোধনাগারগুলি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নায়ার এনার্জি, যার এক বড় অংশীদার রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রসনেফ্ট, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করে। তাদের কায়দাটা ছিল সহজ কিন্তু দারুণ কার্যকর- রাশিয়া থেকে বিপুল ছাড়ে অপরিশোধিত তেল আমদানি করো, নিজেদের অত্যাধুনিক শোধনাগারে তা পেট্রোল, ডিজেল ও জেট ফুয়েলের মতো পরিশোধিত পণ্যে রূপান্তরিত করো, এবং তারপর সেই পণ্যগুলি চড়া দামে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো বাজারে রপ্তানি করো। দেশের লাভ নয়, রিলায়েন্সের লাভ, নায়ার এনার্জির লাভ, যে নায়ার এনার্জির অন্যতম অংশীদার হল কেসানি এনার্জি, কার টাকা খাটে সেখানে? সে আর বলতে হবে নাকি? মজার বিষয় হল, এই দেশগুলোই, মানে যারা এই তেল কিনছিল, তারাই রাশিয়ার উপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। কার্যত, ভারতের বেসরকারি শোধনাগারগুলো, মানে মুকেশ আম্বানি রাশিয়ার তেলকে শোধন করে পশ্চিমা দেশেই পাঠিয়ে দিচ্ছিল, যা মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষায় ছিল ‘ক্রেমলিনের লন্ড্রোম্যাট (Laundromat For The Kremlin) বা টাকা পাচারের এক ব্যবস্থা। এই ব্যবসায়িক মডেলের মুনাফার পাহাড় জমে ওঠে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের মতে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারতীয় সংস্থাগুলি ১৬ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত মুনাফা করেছে। এর সিংহভাগই পেয়েছে রিলায়েন্স এবং নায়ার। রিলায়েন্সের জামনগর শোধনাগার একাই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন ডলারের পরিশোধিত পণ্য রফতানি করেছে, যার মধ্যে আনুমানিক ৪২ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য গিয়েছে সেইসব দেশে যারা রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল। একইভাবে, নায়ার এনার্জি, যারা আগের বছর লোকসানে চলছিল, ২০২২ সালের জুন ত্রৈমাসিকে রেকর্ড পরিমাণ লাভ করে। এই অভাবনীয় লাভের মূল কারণই ছিল সস্তা রাশিয়ান তেল।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিএ পাশ? এমএ পাশ? না ক্লাস টেন পাশ?
কিন্তু তারা যখন ফুলে ফেঁপে লাল তখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর কী অবস্থা? যখন রিলায়েন্স এবং নায়ারের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলি মুনাফার জোয়ারে ভাসছিল, তখন ইন্ডিয়ান অয়েল (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (HPCL) মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো লাভের বদলে লোকসানে চলছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও তারা সেই অনুপাতে দাম বাড়াতে পারেনি, যাতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ না বাড়ে। এর ফলে তাদের বিপুল লোকসান বহন করতে হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারি সংস্থাগুলির উপর এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের বেশিরভাগটাই আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া দামে রফতানি করে মুনাফা করেছে। এটা হল মোদিজির সেই ‘না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা’ বাওয়ালের ফল।
আসুন দেখে নিই লাভ-লোকসানের খতিয়ান: বেসরকারি বনাম রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি (২০২২-২০২৫) মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স কত টাকা লাভ করেছিল? ২০২২-এ ২১৯, ২০২৩-এ ৪২৮, ২০২৪-এ ৪১৯, আর ২০২৫-এ ৬০৯ বিলিয়ন ডলার লাভ করেছে, মানে রিলায়েন্সের লাভ বেড়েছে। রাশিয়ান কোম্পানি ভারতে কাজ করে নায়ার, পিছনের লোকজন অবশ্যই আলাদা, তারা ২০২২-এ ৯৫, ২০২৩-এ ২২৬, ২০২৪-এ ২৭৩, আর ২০২৫-এ ২৭২ বিলিয়ন ডলার কামিয়েছে। মানে তারা তাদের লোকসান ধুয়ে এক বিরাট লাভের মুখ দেখেছে। এবারে আসুন আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কথায়, ইন্ডিয়ান ওয়েল ২০২২-এ ১৯৯, ২০২৩-এ ৪৭৩, ২০২৪-এ ৩৪৬ আর ২০২৫-এ ২৯৪ বিলিয়ন ডলার রোজগার করেছে, মানে তাদের লাভ কমেছে। ভারত পেট্রোলিয়াম ২০২২-এ ১২২, ২০২৩-এ ২৯৩, ২০২৪-এ ২৬৯, ২০২৫-এ ২১৯ বিলিয়ন ডলার রোজগার কমেছে মানে আম্বানির আয় দ্বিগুণ বাড়ল, আর দেশের আয় কমেই যাচ্ছে। হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম ২০২২-এ ৩৪, ২০২৩-এ ৯৫, ২০২৪-এ ১৬৯, আর ২০২৫-এ ৮৫ বিলিয়ন ডলার রোজগার করেছে মানে এই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থারও রোজগার কমেছে। আচ্ছা সাধারণ মানুষের পকেটের কী হাল? সস্তার তেল কি দামে স্বস্তি এনেছে? সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছিল যে, রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কেনার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া। কিন্তু তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে এক সম্পূর্ণ উল্টো গল্প। তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে যখন ভারত বিপুল ছাড়ে রাশিয়ান তেল আমদানি করছিল, তখন দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রায় একই ছিল। দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ২০২২ সাল থেকে প্রায় একই জায়গায় থেকেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র মার্চ ২০২৪-এ পেট্রোল ও ডিজেলের দামে লিটার প্রতি মাত্র ২ টাকা কমানো হয়েছিল, যা ছিল নগণ্য।
মানে খুব পরিষ্কার- অপরিশোধিত তেল কেনার খরচ কমার যে বিপুল সুবিধা, তা সাধারণ মানুষের পকেট পর্যন্ত পৌঁছয়নি। যখন কাঁচামালের দাম ব্যাপকভাবে কমেছে, তখন দাম কমানো হল না কেন? যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ে, তখন সরকার খুচরো দাম বাড়িয়ে দেয় এবং এর কারণ হিসেবে বিশ্ববাজারকে দায়ী করে। কিন্তু যখন রাশিয়ার তেলের কারণে ভারতের জন্য অপরিশোধিত তেলের গড় দাম কমে গেল, তখন সেই যুক্তি উল্টে দিয়ে খুচরো দাম কমানো হল না, বরং স্থিতিশীল রাখা হল। সাধারণ মানুষ দুভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—যখন দাম বেড়েছে, তখন তাদের বেশি টাকা দিতে হয়েছে; আর যখন দাম কমার কথা ছিল, তখন তারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাহলে এই সস্তা তেলের লাভের অংশটা গেল কোথায়? সিংহ ভাগ গিয়েছে মুকেশ আম্বানির পকেটে। আজ প্রধানমন্ত্রী চাপে পড়ে দেশপ্রেমিক সাজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেই মুখোশের পিছন থেকে বিশ্বাসঘাতক সাভারকার আন্ড কোম্পানির বিশ্বাসঘাতকতাই বেরিয়ে আসছে।