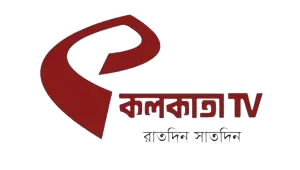মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ ঘোষণা করলেন যে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বা ট্যারিফ চাপানো হবে, তখন নয়াদিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে যেন একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। হ্যাঁ, এইভাবেই থ্রিলার নভেল শুরু হয়। কিন্তু শুধু তো ২৫ শতাংশ নয়, এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো এক অজানা ‘পেনাল্টি’ বা জরিমানার হুমকিও, কাজেই হিমেল স্রোতের সঙ্গে বরফ পড়ছে। এই আকস্মিক আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের পিছনে ট্রাম্প দুটো প্রধান কারণ দেখিয়েছিলেন। প্রথমত, তাঁর অর্থনৈতিক অভিযোগ— ভারতের নিজের শুল্কের হার ‘অনেক বেশি’ এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রয়েছে ‘আপত্তিকর বাধা’। দ্বিতীয়ত, ভূ-রাজনৈতিক শাস্তি— ইউক্রেন যুদ্ধের আবহেও ভারতের রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে শক্তি, মানে তেল, গ্যাস ইত্যাদি আর সামরিক সরঞ্জাম কেনা, যাকে ট্রাম্প নট গুড ‘একেবারেই ভালো নয়’ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই পদক্ষেপ কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, বরং ট্রাম্পের বৃহত্তর ‘লিবারেশন ডে’ বাণিজ্য কৌশলেরই এক অংশ, যার মূল উদ্দেশ্যই হল উচ্চ শুল্কের চাপ তৈরি করে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তিগুলোকে নতুন করে সাজানো। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড-এর এই ঘোষণার পর ভারত সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত মাপা এবং সতর্ক। বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে যে তারা এর ‘প্রভাব খতিয়ে দেখছে’ এবং এক ‘ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ’ চুক্তির বিষয়ে আশাবাদী। কিন্তু সরকারের এই শান্ত প্রতিক্রিয়ার ঠিক উল্টো ছবি দেখা গেল বিরোধী শিবিরে। কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো একযোগে একে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কূটনীতির এক বিরাট ব্যর্থতা বলে আক্রমণ শানাল, সেটাও প্রত্যাশিত।
আসুন একটু বোঝার চেষ্টা করি এই শুল্কের খাঁড়া ভারতীয় অর্থনীতির কতটা গভীরে ক্ষত তৈরি করবে? কেন চীন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও ভারত এতটা অসহায় বোধ করছে? প্রথম অধ্যায়: শুল্কের খাঁড়া: ভারতীয় অর্থনীতি কতটা রক্তাক্ত হবে? ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত ২৫ শতাংশ শুল্ক ভারতের জন্য একটি বিরাট ধাক্কা, কারণ এই হার ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে অনেকটাই বেশি। যেমন, ভিয়েতনামের উপর প্রস্তাবিত শুল্কের হার ২০ শতাংশ। এই ব্যবধান আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যকে সরাসরি প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে দেবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় চিন্তার কারণ হলো রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য চাপানো অতিরিক্ত ‘পেনাল্টি’ বা জরিমানা, যার পরিমাণ বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়নি, সেটা কত বড় হতে পারে তা নিয়েই চিন্তিত নর্থ আর সাউথ ব্লক। এই অস্পষ্টতা ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং সরকারের জন্য এক চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, আজকের শেয়ার বাজারের দিকে তাকালেই মালুম হবে। কারণ, মোট ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করা বা তার মোকাবিলায় সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই জরিমানা আসলে এক অর্থনৈতিক অস্ত্র বা চেয়েও বেশি, এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ যা ভারতকে আলোচনার টেবিলে দুর্বল করে রাখার এক কৌশল হলেও হতেই পারে। যদি খতিয়ে দেখা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে এই শুল্কের আঘাত শুধুমাত্র বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রচেষ্টা নয়, বরং এটা ভারতের সার্বভৌম বিদেশ নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার নোংরা প্রচেষ্টা। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু দশকের পুরনো এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অর্থ হল, আমেরিকা ভারতকে শুধু বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে দেখছে না, বরং তার বিদেশ নীতি কন্ট্রোল করতে চাইছে। এই পদক্ষেপ ভারতের চিরাচরিত জোট-নিরপেক্ষ নীতি এবং কৌশলগত স্বশাসনের ওপর এক সরাসরি আক্রমণ। ঠিক যেভাবে উনি বলেই চলেছেন উনি যুদ্ধ থামিয়েছেন, সেইভাবেই উনি কাশ্মীরে নাক গলাবেন, সেইভাবেই উনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে দেবেন। তো কোথায় সবথেকে বেশি রক্তক্ষরণ হবে?
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | রাজা, তুই ন্যাংটো কেনে?
এই ২৫ শতাংশ শুল্কের প্রভাব পড়বে ভারতের প্রায় ৮৭ বিলিয়ন ডলারের রফতানির উপর, কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মণি-মুক্ত আর গয়না: এই শিল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রফতানি করে, যা আমেরিকার জন্য এই শিল্পের বৃহত্তম বাজার। জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল সতর্ক করেছে যে এই শুল্কের ফলে সাপ্লাই চেন ভেঙে পড়বে, পণ্যের দাম বাড়বে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন হবে। ফার্মাসিউটিক্যালস: ভারত আমেরিকার জেনেরিক ওষুধের সবচেয়ে বড় জোগানদার, যার বার্ষিক রফতানির পরিমাণ প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। সান ফার্মা, ডঃ রেড্ডির মতো বড় সংস্থাগুলো তাদের মোট আয়ের ৩০ শতাংশের বেশি মার্কিন বাজার থেকে আয় করে। মজার বিষয় হল, আমেরিকার প্রতি ১০টি প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ৪টি ভারতের তৈরি ওষুধ দিয়ে পূরণ করা হয়, যা মার্কিন স্বাস্থ্যখাতে ট্রিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে। ফলে এই শুল্ক শেষ পর্যন্ত মার্কিন রোগীদের উপরেই বোঝা হয়ে ফিরতে পারে। বস্ত্র, পোশাক ও চামড়া: এই শ্রমনিবিড় শিল্পগুলো, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গ্যাপ, ওয়ালমার্টের মতো বড় মার্কিন সংস্থাগুলো ভারত থেকে পোশাক আমদানি করে। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশগুলো ইতিমধ্যেই কম শুল্কের সুবিধা পায়। এর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ভারতের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা প্রায় শেষ করে দেবে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে হওয়া চুক্তিতে ১৬ শতাংশ শুল্ক মকুব হওয়ায় এই শিল্প কতটা শুল্ক-সংবেদনশীল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ইলেকট্রনিক্স ও গাড়ির যন্ত্রাংশ: এই শুল্ক ভারতের স্মার্টফোন উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে ওঠার স্বপ্নকে ধাক্কা দেবে, যা ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর পাশাপাশি প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের গাড়ির যন্ত্রাংশ রফতানির বাজারও বিপদে পড়বে। কৃষি ও সামুদ্রিক পণ্য: এই শুল্ক ভারতের সামুদ্রিক পণ্য, বিশেষ করে চিংড়ি রফতানিতে বড় প্রভাব ফেলবে, যেখানে ইকুয়েডরের মতো দেশগুলো ভারতের প্রধান প্রতিযোগী। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে কৃষক ও মৎস্যজীবীদের উপর, যা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়। এই শুল্কের আঘাতের মূল লক্ষ্য শুধু কয়েকটা পণ্য নয়, বরং এটা মোদি সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI) স্কিমের মূলে আঘাত হানার এক প্রচেষ্টা। যে ক্ষেত্রগুলোকে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের স্তম্ভ হিসেবে দেখা হচ্ছিল, ঠিক সেই ক্ষেত্রগুলোকেই টার্গেট করা হয়েছে। এটা ভারতের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার কৌশলগত চাল।
এবারে আসুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। চীনের প্রাচীর বনাম ভারতের নড়বড়ে বেড়া: ট্যারিফ যুদ্ধে কে কীভাবে লড়ছে? ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের মুখোমুখি চীনও হয়েছিল, কিন্তু তারা যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, তার সঙ্গে ভারতের প্রতিক্রিয়ার তুলনা করলেই বোঝা যায় কেন ভারত আজ এতটা বেকায়দায়। চীন যখন মার্কিন শুল্কের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন তারা কয়েকটা সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাৎক্ষণিক ও সুনির্দিষ্ট পাল্টা আঘাত: চীন কোনও দ্বিধা না করে আমেরিকার উপর পাল্টা শুল্ক চাপিয়েছিল। তারা এমন সব পণ্যকে নিশানা করেছিল, যা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল— যেমন সয়াবিন এবং শূকরের মাংস। এর ফলে ট্রাম্পের নিজের ভোটব্যাঙ্কেই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সাপ্লাই চেনের ক্ষমতাকে ব্যবহার: এটাই ছিল চীনের তুরুপের তাস। চীন বিশ্বের কারখানা হওয়ায় মার্কিন সংস্থাগুলো তাদের উৎপাদনের জন্য চীনা যন্ত্রাংশের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে চীনা পণ্যের উপর শুল্ক চাপানোর অর্থ ছিল মার্কিন সংস্থাগুলোর উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে আমেরিকার ভিতরেই এক বা একের বেশি শক্তিশালী ব্যবসায়ী লবি তৈরি হয়, যারা এই শুল্ক তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুরক্ষা: বেজিং তার শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানোর জন্য স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করেছে এবং মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে শুল্কের আঘাতের একটি বড় অংশ শুষে নিয়েছে, মানে তার কোনও প্রভাবই পড়েনি। আর তার সঙ্গে চীন আমেরিকার উপর নির্ভরতা কমাতে দ্রুত তাদের বাণিজ্য ইউরোপ এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) ভুক্ত দেশগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এবং হাতের শেষ তাস হিসেবে চীন তার হাতে থাকা কৌশলগত সম্পদ, যেমন রেয়ার আর্থ মিনারেলস-এর উপর রফতানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আমেরিকাকে তাদের নির্ভরশীলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের পক্ষে চীনের মতো করে লড়াই করা প্রায় অসম্ভব। এর পিছনে কয়েকটি কাঠামোগত কারণ রয়েছে: অর্থনৈতিক শক্তির ফারাক: চীনের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বড় (১৯.২ ট্রিলিয়ন ডলার বনাম ৪.২ ট্রিলিয়ন ডলার)। এই বিপুল আকার চীনকে এমন অর্থনৈতিক ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা দেয়, যা ভারতকে ভেঙে দিতে পারে। উৎপাদন বনাম পরিষেবা: চীনের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল উৎপাদন শিল্পের উপর, যা তাদের পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য যুদ্ধে বাড়তি সুবিধা দেয়। অন্যদিকে, ভারতের বৃদ্ধি মূলত পরিষেবা-নির্ভর। ভারতের উৎপাদন শিল্প তুলনামূলকভাবে ছোট এবং বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেনের সঙ্গে চীনের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। তাই ভারতের সেই ক্ষমতা নেই যা চীনের ছিল। অসংগঠিত অর্থনীতির বোঝা: ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মশক্তি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। এই শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও আর্থিক সুরক্ষা বা সরকারি সহায়তা নেই। ফলে রফতানিতে বড় আঘাত এলে তাদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেক বেশি ভঙ্গুর করে তুলেছে। বাণিজ্য ঘাটতি: ভারতের একটি স্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, যেখানে চীনের বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং লড়াই করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতি থেকে এক বিষয় কিন্তু স্পষ্ট: leverage বা ক্ষমতার ভারসাম্যে ভারত ও চীনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। চীনের রফতানি করা পণ্যগুলো ছিল মার্কিন সংস্থাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ। তাই চীনের উপর শুল্ক চাপানো মানে ছিল মার্কিন উৎপাদন শিল্পের উপর কর চাপানো । কিন্তু ভারত থেকে রফতানি হওয়া বেশিরভাগ পণ্যই হল চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য— যেমন পোশাক, গয়না বা ওষুধ। ভারতের শার্টের উপর শুল্ক বাড়লে মার্কিন ক্রেতার পকেটে টান পড়ে, কিন্তু কোনও মার্কিন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় না। ক্ষমতার এই অসামঞ্জস্যই ভারতের আলোচনার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাহলে কী? তাহলে হাতে পেনসিল। এই ট্যারিফ লাগু হলে, তার উপরে পেনাল্টি চড়লে মোদিজির মেক ইন ইন্ডিয়া মুখ থুবড়ে পড়বে এবং মানুষের কাছেও নরেন্দ্র মোদির বিদেশনীতির ব্যর্থতার ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক নির্বোধ মিথ্যেবাদী রাজার হাতে দেশ চলে গেলে দেশকে আর দেশের মানুষকে যে খেসারত দিতেই হবে তা তো সবার জানা কথা।