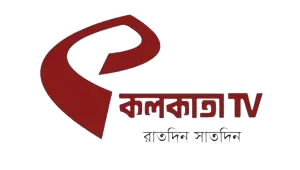জল বাড়ছে, এখনও যদি আমরা উঠে না বসি, আমরা এখনও যদি চুপ করে বসে থাকি, তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা ডোডো পাখি হয়ে যাবে, বাংলা ভাষার কবি, লেখক, চলচিত্র পরিচালক থেকে গায়ক নায়ক মিউজিয়মে ঠাঁই পাবেন। আর তার চেয়েও বড় কথা রাজ্যের কোটি কোটি গ্রাম মফস্সলের, শহরের বস্তি অঞ্চলের কম সুযোগ পাওয়া ছেলেমেয়েরা আর কোনওদিনও চাকরি পাবে না, ভাববেন না যে তার বদলে অন্য রাজ্যে গিয়ে মজদুরি করে দিন কাটানো যাবে, যাবে না কারণ সেখানেও তাড়া করছে পুলিশ। অতএব, জল বাড়ছে, সাধু সাবধান। আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করছিল, তাহলে কী করব? শুরুটা কী করে হবে? আজ নিশ্চয়ই আলোচনা করব, কেন কীভাবে এই হিন্দি রাজের সূচনা হল, আলোচনা করব এর পিছনের রাজনীতি নিয়ে, কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট কাজ যা আমরা এখনই শুরু করতে পারি। তা হল, সপ্তাহে একটা দিন কেবল বাংলা, হাটে, মাঠে, ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, প্লেনে বাঙালি একদিন বাংলাতেই কেবল বাংলাতেই কথা বলবে। বাঙালির সঙ্গে, অবাঙালির সঙ্গে, অফিসে, কলেজে, স্কুলে কোর্ট কাছারিতে কেবল বাংলা। ঠিক আছে হুজুরই বলব, কিংবা হুজুর মাই বাপ বলব, কিন্তু মি লর্ড বলব না। এতে কী হবে? সেঁকে যাবে। হ্যাঁ, এই ঘাড়ে চেপে হিন্দি চাপানেওলারা সেঁকে যাবে। বাংলা পক্ষ, প্রতিপক্ষ থেকে পরিষদ, অপরিষদ, সবার কাছে, বাংলার প্রতিটা মানুষ যাঁরা বাংলা বলেন, তাঁদের কাছে আবেদন, একবছর করুন, একটা বছর, দেখবেন আশেপাশের আবহাওয়া অনেক অনেক ভালো হয়ে গেছে।
গত ১১ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে যে সরকার চলছে, সেই গোটা সময় ধরেই ‘হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থান’ নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। আগেও ছিল, তবে এবার এর কায়দাটা আগের থেকে অনেকটা আলাদা। ১৯৬৫ সালের মতো সরাসরি আইন করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বদলে, এখন অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং কায়দা করেই এই হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কায়দাটাকে প্রত্যক্ষ ‘চাপানো’ (imposition)-র বদলে পরোক্ষ “প্রাধান্য” (promotion) এবং “স্বাভাবিকীকরণ” (normalization)-এর এক চালাকি বলা যেতে পারে। এই নতুন কায়দার এক বড় উদাহরণ হল জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০। কাগজে-কলমে এই নীতি কোনও রাজ্যের উপর হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছে না। এটা এক আপাত নিরীহ ত্রি-ভাষা নীতির কথা বলে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তিনটি ভাষা শিখবে, যার মধ্যে অন্তত দুটি হতে হবে ভারতীয়। কিন্তু এখানেই আসল সমস্যাটা লুকিয়ে আছে। বাংলা, কেরালা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর মতো অ-হিন্দি রাজ্যগুলো মনে করছে এটা আসলে হিন্দিকেই চাপিয়ে দেওয়ার একটা ঘুরপথ রাস্তা। কারণ, বেশিরভাগ অ-হিন্দি রাজ্যে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা যেমন বাংলা, ওড়িয়া বা কন্নড় শেখানোর মতো পরিকাঠামো বা শিক্ষক নেই। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে হিন্দি শেখাটাই একমাত্র সহজ বিকল্প হয়ে দাঁড়াবে। মানে বাংলায় বসবাসকারী এক তামিল পরিবারের সন্তানকে হিন্দি শিখতে হবে, তেমনি কেরালায় বসবাস করে এমন এক বাঙালিকেও হিন্দিই শিখতে হবে।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | বাংলা এগোচ্ছে, মমতা বলছেন না, নীতি আয়োগ বলছে
এভাবেই যা কাগজে-কলমে ঐচ্ছিক, তা বাস্তবে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি, সরকারি কাজে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রেও হিন্দিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বিভিন্ন সময়ে সরকারি দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলোতে হিন্দির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এমনকী ২০১৪ সালে, পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের আমলে জারি করা এক সার্কুলারকে নতুন করে লাগু করে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকারি কর্মকর্তারা যেন টুইটার, ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিও ব্যবহার করেন এবং হিন্দিকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়। সরকারি বিজ্ঞাপন এবং ওয়েবসাইটেও এখন হিন্দির ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। হিন্দি প্রসারের এই নীতিগত পদক্ষেপের পাশাপাশি চলছে প্রতীকী জাতীয়তাবাদের প্রয়োগ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সমস্ত বড় প্রকল্পের নাম এখন হিন্দিতে রাখা হয়, যেমন – ‘প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা’, ‘উজ্জ্বলা যোজনা’, ‘মেরা যুবা ভারত’ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সারা দেশে, এমনকি অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলেও, হিন্দিকে প্রশাসনিক এবং জাতীয়তার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার একটি ঘুরপথ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই গোটা প্রক্রিয়াতে বিজেপির আদর্শগত চালিকাশক্তি, আরএসএস-এর ভূমিকা খুব ইন্টারেস্টিং আর দু-মুখো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আরএসএস-এর ভূমিকার কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, করছেন। আরএসএস-এর মূল আদর্শই হল ‘হিন্দুত্ব’ এবং এক হিন্দু রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু ভাষা বিতর্কের ক্ষেত্রে আরএসএস এক কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে, যাকে বলে গোলগোল অবস্থান। একদিকে যখন বিজেপি সরকার প্রশাসনিক স্তরে হিন্দি প্রসারের নীতি গ্রহণ করছে, তখন আরএসএস-এর শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন যে, ‘ভারতের সব ভাষাই রাষ্ট্রভাষা’ এবং তাঁরা কোনও একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী। এটা এক গট আপ গেম, যেখানে দুটো সংগঠনের মধ্যে এক শ্রম বিভাজন division of labor কাজ করছে। সরকার কঠোর এবং বিতর্কিত নীতিগুলোকে মাঠে নামাচ্ছে, প্রয়োগ করছে, আর আরএসএস উল্টোদিকে নরম, সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা দিয়ে অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং সেখানকার প্রতিরোধকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। এর আরেকটা উদাহরণ হল, আরএসএস-এর নেতারা ‘ইন্ডিয়া’ নামের পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘ভারত’ নাম ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেন, আসলে তাঁরা এটাকে ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে সেই ঘুরিয়ে নাক দেখানোর ব্যবস্থা করে। ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই ‘কাশী-তামিল সঙ্গমম’-এর মতো অনুষ্ঠানের আয়োজনও এই কৌশলেরই অংশ। প্রধানমন্ত্রী মোদি মুখে বলেন যে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু আসলে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো এক দারুণ কায়দাবাজি, দেখো আমি তো জাতীয় সংহতির কথা বলছি ইত্যাদি, যার আসল উদ্দেশ্য হল দক্ষিণের সংস্কৃতিকে উত্তর ভারতের বৃহত্তর হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ভাষার প্রতিরোধের ধার কমিয়ে দেওয়া।
‘এক দেশ, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি’- এই ধারণাটাও তো ওই আরএসএস–বিজেপির। ভারতের মতো একটি বৈচিত্র্যময় দেশের জন্য এর পরিণতি মারাত্মক হবেই। এই নীতি শুধুমাত্র কয়েকটা ভাষার উপর আঘাত হানে না, এটা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক সম্প্রীতি এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দেয়। ভারতের সংবিধান কী বলছে? ভাষা আর শিক্ষা মূলত রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। তাই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোনও একটা ভাষাকে, এক্ষেত্রে হিন্দিকে, সারা দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা সরাসরি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির (federalism) মূল ভাবনার বিরোধী। যখন কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) না মানার ‘অপরাধে’ তামিলনাড়ুর মতো একটি রাজ্যের প্রাপ্য আর্থিক অনুদান আটকে দেওয়ার হুমকি দেয়, তখন তা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কতে নিজেদেরকে এক অত্যাচারী জমিদার হিসেবে খাড়া করে। রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসনের উপর এক সরাসরি হস্তক্ষেপ হয়ে ওঠে কাজেই প্রতিরোধ শুরু হয়। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এই মূর্খের মতো প্রচেষ্টা শুধুমাত্র তামিল, বাংলা, কন্নড় বা মালয়ালমের মতো প্রধান অ-হিন্দি ভাষাগুলোর জন্যই বিপজ্জনক নয়, এটা হিন্দি বলয়ের ভেতরের ভাষাগত বৈচিত্র্যকেও ধ্বংস করছে। ভোজপুরি, মৈথিলি, ব্রজভাষা, আওয়াধি, রাজস্থানি, ছত্তিশগড়ির মতো বহু সমৃদ্ধ এবং স্বতন্ত্র ইতিহাস সম্পন্ন ভাষাকে জনগণনায় ‘হিন্দি’র উপভাষা হিসেবে দেখানো হয়, যারা এই কাজ করছে তার হয় মূর্খ নয় শয়তান। যে রামচরিতমানস আওয়ধি ভাষাতে লেখা হয়েছিল তা হিন্দির উপভাষা? আর এই ধরনের শয়তানির ফলে এই ভাষাগুলো তাদের নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে এক কৃত্রিম, সংস্কৃত শব্দবহুল ‘শুদ্ধ হিন্দি’, যা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা থেকে অনেক দূরে। ফলে, হিন্দি আগ্রাসনের শিকার শুধু অ-হিন্দিভাষীরাই নয়, হিন্দি বলয়ের কোটি কোটি মানুষও, যাঁদের মাতৃভাষাকে হিন্দির ছায়ায় তলায় অন্ধকার ঘরে পুরে দেওয়া হচ্ছে। ভাষা তো শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটা শিক্ষা, প্রশাসন এবং ভালো বেতনের চাকরিতে ঢুকে পড়ার চাবিকাঠিও বটে। যদি হিন্দিকেই প্রশাসনিক কাজ এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রধান ভাষা করে তোলা হয়, তবে দেশের কোটি কোটি অ-হিন্দিভাষী নাগরিক অটোম্যাটিকালি এক অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন, ফলে এক নতুন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে। তামিলনাড়ুর এক মন্ত্রী যে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, “হিন্দি শিখে কি আমাদের ছেলেরা কোয়েম্বাটুরে এসে পানিপুরি বিক্রি করবে?” সেই উক্তি আসলে এই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক আশঙ্কারই প্রতিফলন। এর মানে হল, হিন্দি না জানলে ভালো চাকরি বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে আর শুধুমাত্র কম মাইনের কাজে থাকবে তাদের জন্য? ভারতের আসল শক্তি তার ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ unity in diversity-তে। এই বৈচিত্র্যকে নষ্ট করে জোর করে uniformity চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করার বদলে আরও দুর্বল করে দেবে।
ভাষা মানুষের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যখন কোনও ব্যক্তির ভাষার উপর আঘাত আসে, তখন তা তার আত্মমর্যাদাকে আহত করে এবং তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করে। মহারাষ্ট্রে যখন স্কুলশিক্ষায় হিন্দি বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হয়েছিল, তখন শিবসেনার দুই বিবদমান গোষ্ঠী উদ্ধব ঠাকরে এবং রাজ ঠাকরে একসাথে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে, এমনকী তারা তাদের বিরোধ মিটিয়েও নিয়েছে। ভাষার গর্ব আজও ভারতের রাজনীতিতে এক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং শক্তিশালী বিষয়, এবং একে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। ‘হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থান’- এই স্লোগানের যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের এক বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভাষা ও ধর্মকে একসূত্রে বেঁধে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করা। আজ, একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই একই গোলমেলে স্লোগান, আদর্শ এক নতুন চেহারায়, নতুন এবং আরও সূক্ষ্ম কায়দায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এটা অহিন্দিভাষীদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ, আমরা বাঙালিরা সেই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম, শুরু হোক প্রতিরোধ আর তার শুরুয়াত হোক একটা ছোট্ট কাজ দিয়ে, আসুন সপ্তাহে একদিন মাত্র এক দিন আমরা বাংলা, বাংলাতেই কথা বলি, সব্বার সঙ্গে, সব জায়গায়।