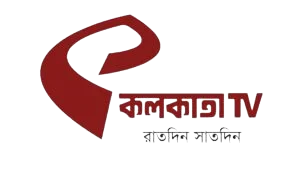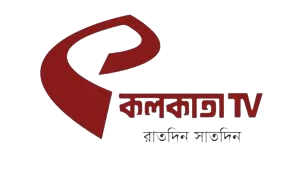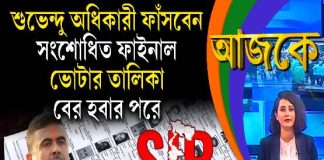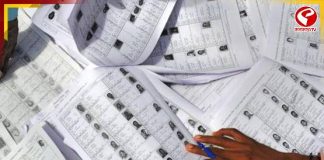ট্রাম্প হুজুরের সব নির্দেশ মেনেই রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে, কৃষি বাজারের দরজা খানিক ফাঁক করে একটা ডিল হয়েই যেতে পারে আমেরিকার সঙ্গে। সেই ডিলে ট্যারিফ কমতেও পারে। কিন্তু সেসব তো এক সাময়িক স্বস্তি, এই মুহুর্তে বিশ্ব কূটনীতির মঞ্চে ভারত এত একলা কেন? এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? ভারত এই মুহুর্তে এক অদ্ভুত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে দেশের অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অ্যাটলিস্ট সেই বৃদ্ধির ঢাক তো সজোরেই বাজানো হচ্ছে। না মাথা পিছু আয় বাড়ছে না, গরীব আর বড়লোকের বৈষম্য কমার বদলে তা আরও বেড়েই চলেছে। মাত্র ক’দিন আগে জি-টয়েন্টির এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের এক শতাংশ অতি ধনীদের সম্পদ বেড়েছে ৬৩ শতাংশ হারে। কিন্তু এই আপাত বৃদ্ধির আবহে আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আঞ্চলিক কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা যাকে বিফলতা বললে ভালো হয়। যেখানে ভারত নিজেকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে, সেখানে তার অর্থনৈতিক কূটনীতি কেন বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছে? এই প্রশ্নটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ঠিক উল্টোটা হওয়ার কথা ছিল, এক গ্রোইং মার্কেটের জন্য অনেক শর্ত পাশে সরিয়েই অর্থনৈতিক চুক্তিগুলো হওয়ার কথা বদলে নতুন নতুন শর্ত চাপছে আমাদের ঘাড়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আর শি জিনপিং, যারা তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধে একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শুল্কের অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, এ ৫০ শতাংশ চাপায় তো সে ১০০ শতাংশ! এরকমই চলছিল, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে এক বাস্তববাদী চুক্তিতে পৌঁছতে পারলেন। যা দু’জনেই ‘উইন-উইন’ বলেই মনে করছেন। অথচ ভারত এখনও আমেরিকার সঙ্গে এক সামান্য বাণিজ্য চুক্তির জন্যও দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছে। কেন এই পার্থক্য? কেন ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজ কার্যত একা?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এশিয়ান সম্মেলন এড়িয়ে গেলেন আর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত অচলাবস্থা। এই দু’টো ঘটনা খতিয়ে দেখলে সাফ বোঝা যায় যে, ভারতের বিদেশনীতি আজ আন্তর্জাতিক লেনদেনমূলক বাস্তববাদের (Transactional Pragmatism) মুখে একধরণের অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণবাদ আর কূটনৈতিক ব্যর্থতার শিকার। আচ্ছা, এশিয়ান মঞ্চে কেন ট্রাম্পের মুখোমুখি হতে চাইলেন না মোদি? প্রধানমন্ত্রী মোদি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে সশরীরে যোগ না দিয়ে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন, যেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইচ্ছে করেই ট্রাম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য মুখোমুখি হওয়াটাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এই পিছু হঠার প্রধান কারণ কী? কোন অপরাধ তিনি করেছেন যে, ট্রাম্পের সামনে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না? তাহলে কি ট্রাম্প সত্যি কথা বলছেন? তাহলে কি ট্রাম্প এর মধ্যস্ততাতেই ভারত–পাক যুদ্ধ থেমেছিল? যদি তা নাই হয়, এক জোকার যদি মিথ্যের পর মিথ্যে বলতেই থাকে, তার সামনে দাঁড়িয়েই তো খোলসা করা উচিত ছিল যে, এরকম কিছু হয়নি। এই সিদ্ধান্থীনতার ফলে কী হল? ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর প্রথমে ২৫ শতাংশ, পরে বাড়িয়ে মোট ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ট্যারিফ চাপিয়ে দেয়। এই শুল্ক আরোপের মূল অজুহাত ছিল ভারতের রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখা, যা আমেরিকা ভালোভাবে নেয়নি। এই বিরাট ট্যারিফ ভারতের রফতানি বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে, সরাসরি ট্রাম্পের মুখোমুখি হওয়া জরুরি ছিল, আর এক জটিল চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য কঠিন দর কষাকষি করা ছিল পথ। কিন্তু যদি ট্রাম্পের কথাই সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এই ফেসঅফ-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হত জনসমক্ষে আরও কঠোর সমালোচনা হজম করা, তাও আবার বিহার নির্বাচনের সামনে। দেশের ভেতরে নির্বাচনের আগে মোদি সরকার এমন কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারত না। মোদিজির ৫৬ ইঞ্চির ভাবমূর্তিতে ফিনাইল ছেটানো হত।
কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ উচ্চ-স্তরের কূটনীতিতে দেশের কূটনৈতিক দৃঢ়তার অভাবকেই তুলে ধরল। যখন দু্টো দেশ শুল্কের মতো গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, তখন সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সরাসরি আলোচনার টেবিলে এসে হয় চুক্তি করতে হয়, নয়তো কঠোর অবস্থান নিতে হয়। সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক স্বস্তি দিলেও এটা বলে দেয় যে, ভারত বড় অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাসী নয়। যেখানে ট্রাম্প নিজেই একটা লেনদেনমূলক চুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেমনটা আমরা চীনের ক্ষেত্রে দেখলাম, মোদির এই এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব এক শক্তিশালী আর ফলপ্রসূ আলোচনার সুযোগ হাতছাড়া করেছে। অন্যদিকে ট্রাম্প এবং শি জিনপিং-এর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিটার দিকে তাকান, ভারতের চরম নিষ্ক্রিয়তার ঠিক উল্টোদিকে একট চমৎকার উদাহরণ। আমেরিকা এবং চীনের মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক সংঘাত তো চলছিলই, যেখানে তারা একে অন্যের পণ্যের উপর পাল্লা দিয়ে শুল্ক চাপাচ্ছিল। কিন্তু এত বৈরিতা আর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, দুই নেতাই শেষমেষ বাস্তব অবস্থাটা বুঝলেন, চুক্তিতে সই করলেন। ট্রাম্পের লক্ষ্য খুব পরিস্কার ছিল, আমেরিকার কৃষক আর কৃষি শিল্পকে সুবিধা দেওয়া। তিনি তাঁর ট্যারিফ অস্ত্র ব্যবহার করে চীনকে বাধ্য করলেন কিছু অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিতে। শি জিনপিংও জানতেন যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য যুদ্ধ চীনের অর্থনীতির জন্য আরও ক্ষতিকর হবে, তাই তিনি কৌশলগতভাবে নমনীয়তা দেখালেন। চুক্তি হল। আমেরিকা চীনা আমদানিতে শুল্ক কমাল এবং চীন পাল্টা প্রতিশোধমূলক শুল্ক স্থগিত রাখল। এই চুক্তি দেখিয়ে দিল যে, বিশ্ব বাণিজ্য কঠোরভাবে লেনদেনমূলক। ট্রাম্পের নীতি ছিল—“যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার অর্থনীতির জন্য স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য লাভ দেখছি, ততক্ষণ আমি চুক্তি করব না”, আবার দেখুন চীন কিন্তু তাদের চাপানো শুল্ক স্থগিত রেখেছে, মানে প্রয়োজনে আবার তা চাপানোর রাস্তাও তারা খুলে রাখল।
আরও পড়ুন: Fourth Pillar | ভোটের আগেই ফাটে কেন?
তাহলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি কেন থমকে আছে? ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা বেশ কয়েকবার শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা ভেস্তে গিয়েছে। মূল কারণ হল, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার প্রশ্নে ভারতের এক কঠোর অবস্থান। চুক্তিটা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ, ভুল যোগাযোগ এবং এক ধরণের ডোমেস্টিক পলিটিক্সের ইস্যুগুলো কাজ করছে। অচলাবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতের অত্যন্ত সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ খাত, বিশেষ করে কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য। আমেরিকা এই খাতে তাদের জন্য বাজার উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছিল। ভারত এই খাতগুলিতে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বজায় রাখতে চেয়েছিল, কারণ এখানে বিদেশি প্রতিযোগিতা ঢুকলে দেশের বিশাল সংখ্যক কৃষক এবং দুগ্ধ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হতে পারে। এই কারণেই ভারত সরকার এই বিষয়ে কোনওরকম নমনীয়তা দেখাতে পারেনি। এই সুরক্ষা নীতি মোদি সরকারের কাছে অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী রাজনীতির এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতটা ছাড় দিলে চুক্তি হত? কীভাবে এই ছাড় দিয়েও কৃষক স্বার্থ বজায় রাখা যেত? তা নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে, কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা কী করেছেন প্রধানমন্ত্রী? না করেননি। আসলে দেশের প্রত্যেক বিরোধী শক্তি রাজনৈতিক দল আর সংগঠনকে যদি কেউ দেশদ্রোহী মনে করে, তাহলে সেখানে আলোচনাটা শুরুই বা হবে কোথ্বকে? কাজেই পুরো ব্যাপারটা এখন এক স্টেলমেট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারওপরে রাজনৈতিক ফাটলও আলোচনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ট্রাম্পের বারবার পাকিস্তান নিয়ে মধ্যস্থতা করার মন্তব্য ভারতীয় মানুষজনের সামনে মোদিজিকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। এতদিন ধরে বানানো তাঁর ৫৬ ইঞ্চির ভাবমূর্তিতে ফাটল ধরবে, এই ভয়েই তিনিও সম্পর্কের শীতলতা বাড়িয়েছিলেন। এই কূটনৈতিক সংঘাত এবং ব্যক্তিগত শীতলতা বাণিজ্য আলোচনাকে আরও জটিল করে তুলেছে। একাধিক ভারতীয় কর্মকর্তার মতে, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুর্বল কৌশল এবং সঠিক কূটনৈতিক সমর্থনের অভাবও দায়ী। এটি স্পষ্ট করে যে, ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সুযোগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তার সঙ্গে জুড়েছে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতের একাকীত্ব।
ভারত সরকার ‘নেবারহুড ফার্স্ট’ নীতির উপর জোর দিলেও, বাস্তবে নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক বেশ ভঙ্গুর। সীমান্ত বিরোধ, জলের সমস্যা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই সম্পর্কগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে, ভারত তার নিজের দক্ষিণ এশিয়াতেই আজ একঘরে হয়ে পড়ছে। আর সেরকম এক পরিস্থিতিতে চীনের বাড়তে থাকা প্রভাব ভারতকে আরও কোণঠাসা করেছে। চীন তার ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ (BRI)-এর মাধ্যমে বিশাল ঋণ ও পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়ে প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। অন্যদিকে, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় শক্তি হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা এবং ‘বড় ভাই সুলভ অহংকারী আচরণ’ প্রতিবেশীদেরকে চীনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই আঞ্চলিক একাকীত্বের কারণেই ভারত এখন বাধ্য হয়ে লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার মতো দূরবর্তী অঞ্চলে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা খুঁজছে, যা এই অঞ্চলে ভারতের দুর্বল অবস্থানের এক নীরব স্বীকারোক্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতের একলা হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ‘রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ’ (RCEP) নামক চুক্তি থেকে ভারতের সরে আসা। ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভারত এই বৃহৎ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রধান কারণ ছিল দেশিয় শিল্প ও কৃষকদের সুরক্ষা দেওয়া, যারা সস্তা চীনা পণ্যের দ্বারা বাজার হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ছিল। আরসিইপি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য ব্লক। সেখান থেকে সরে আসার ফলে ভারত আঞ্চলিকভাবে এক বিশাল অর্থনৈতিক মঞ্চ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এই সরকারের মাথাতেই এল না যে, আরসিইপি ভারতের জন্য কেবল এক অর্থনৈতিক সুযোগ নয়; এটা ছিল চীনকে এক বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে মোকাবিলা করার আর তার অর্থনৈতিক অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার এক স্ট্রাটেজিক প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু চীনকে মোকাবিলা করার চেয়ে দেশিয় সুরক্ষার দিকে তাকিয়ে ভারত এই মঞ্চ ছেড়ে দিল। এই সিদ্ধান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতের কৌশলগত শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এবং ভারত আরও আরও একলা হয়ে পড়ছে।
দেখুন ভিডিও: