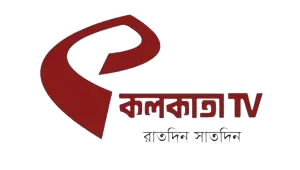এক সাক্ষাৎকারে একবার দারুণ অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন প্রয়াত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সাল। কলকাতা থেকে তিনি প্রথম বিদেশ যাচ্ছেন বিমানে। বিমানটি প্রথমে নামে করাচিতে (Karachi)। তখন ভোর। চারদিকে কুয়াশা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় চোখ। বিশাল একটা হোর্ডিং। তাতে বড় বড় হরফে বাংলায় লেখা করাচি বিমানবন্দর। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। খোদ কলকাতা বিমানবন্দরও তখন বাংলায় লেখা হয়নি। আর অত দূরে, কয়েক হাজার মাইল দূরে, তাও পাকিস্তানে বাংলায় লেখা!
আসলে সুনীল যখন করাচিতে যান, তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর সঙ্গেই ছিল বাংলা (Bengali) ভাষার স্বীকৃতি। তাই করাচি বিমানবন্দরেও ছিল বাংলা ভাষার ব্যবহার। সেটা অবশ্য আপনাআপনি হয়নি। এর পিছনে রয়েছে বহু আত্মত্যাগ, সংগঠিত আন্দোলন। ছিল বরকত, রফিক, জব্বারদের শহীদ হওয়া। সেই একুশের চেতনা ১৯৭১-এ পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। একুশে ফেব্রুয়ারির (Ekushe February) ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশ জুড়ে যে চেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই ফল স্বাধীন বাংলাদেশ।
সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত বোধের প্রকাশ। আর যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলাদেশে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে এবং প্রতিবছর এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, বিশ্বের ১৮৮টি দেশ প্রথমবারের মতো ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করে। ইউনেস্কোর পর রাষ্ট্রসঙ্ঘও দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
একুশের চেতনায় লেখা প্রথম গান-কবিতা-নাটক-সংকলন-উপন্যাস
‘ভুলব না, ভুলব না/ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না।’ রচয়িতা গাজিউল হক। গানটির প্রথম চরণ ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আরমানিটোলা ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় প্রথম গাওয়া হয়। ফি-বছর এই দিনে শহীদ স্মারকের কাছে একটি প্রভাতফেরি হয়। সেখানে গাওয়া হয়, ‘মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে আজিকে স্মরিও তারে। ১৯৫৩ সালে প্রথম শহীদ দিবসের প্রভাতফেরিতে গাওয়া এই গানের রচয়িতা মোশারেফউদ্দিন আহমদ। তিনি এটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ সালে রচনা করেন।
কবিতা
একুশের প্রেরণার প্রথম কবিতা লেখা হয়েছিল চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং সীমান্ত পত্রিকার সম্পাদক মাহবুল উল আলম চৌধুরী একুশের ঘটনার কথা শুনে সেদিনই লিখেছিলেন, ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’। কবিতাটি সে রাতেই চট্টগ্রামের একটি প্রেসে গোপনে ছাপানো হয় এবং পরদিন লালদিঘির মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত ও বিলি হয়। প্রকাশের পরপরই মুসলিম লিগ সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
এরপর অনেকেই রাষ্ট্রভাষা এবং একুশের উপর অনেক কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে কবি শামসুর রাহমানের ‘বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’, ‘আর যেন না দেখি’, আনিস চৌধুরীর ‘একুশের কবিতা’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘একুশের কবিতা’, শহীদুল্লাহ কায়সারের ‘শহীদ মাকে’, রফিক আজাদের ‘পঞ্চানন কর্মকার’, হুমায়ুন আজাদের ‘বাঙলা ভাষা’, নির্মলেন্দু গুণের ‘আমাকে কী মাল্য দেবে দাও’ উল্লেখযোগ্য।
নাটক
নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রেও একুশের চেতনা অসামান্য প্রভাব রেখে গিয়েছে। ভাষা-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার সময়েই এ নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে। ১৯৫১ সালে লেখা আসকার ইবনে শাইখের নাটকটির নাম দুর্যোগ। আসকার ইবনে শাইখ ভাষা আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের নিয়ে লিখেছেন আরেকটি নাটক। নাটকটির নাম ‘যাত্রী’ (১৯৫৪)। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার ‘অপরাধে’ ১৯৫২ সালে জেলে বন্দি ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত ও মুনীর চৌধুরীসহ অনেক লেখক-সাংবাদিক। রণেশ দাশগুপ্ত তখন মুনীর চৌধুরীকে ভাষা আন্দোলনের উপর একটি নাটক লেখার অনুরোধ জানান। ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে তাঁর লেখা বিখ্যাত কবর নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। অভিনয় করেছিলেন বন্দিরাই। পরের বছর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে নাটকটি অভিনীত হয়।
প্রবন্ধ
কবিতার পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিষয়ে লেখা হয়েছে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এর মধ্যে মোজাফফর আহমদের ‘উর্দু ভাষা এবং বঙ্গীয় মুসলমান’, মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘আমাদের ভাষা সমস্যা’, কাজী মোতাহার হোসেনের ‘রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তান ভাষা সমস্যা’, অলি আহাদের ‘নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা’, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার ‘ভাষা নিয়ে কথা’, আবুল হাশেম ফজলুল হকের ‘একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মর্মকথা’ উল্লেখযোগ্য।
সংকলন
একুশের প্রথম সঙ্কলন একুশে ফেব্রুয়ারি। সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান। উৎসর্গপত্রটি লিখে দেন ডঃ আনিসুজ্জামান। সংকলনটিতে প্রকাশিত হয় একুশের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান ইত্যাদি। এই সংকলনটি বাংলাদেশের জাতীয় সচেতনতা বিকাশের প্রথম সাহিত্যিক দলিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এসব সঙ্কলন ও বিশেষ সংখ্যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে।
উপন্যাস
অমর একুশের উপর লেখা প্রথম উপন্যাস জহির রায়হানের ‘আরেক ফাল্গুন’। শহীদ দিবস পালন, একুশের মিটিং-মিছিল, সরকারি বাধা, শহীদ মিনার নির্মাণসহ একুশের স্মৃতিবিজড়িত নানা ঘটনা উপন্যাসটির উপজীব্য। পাঁচের দশকেই এটি পত্রিকায় ছাপা হয়, বই আকারে বের হয় ১৯৬৯ সালে।
চলচ্চিত্র
১৯৭০ সালে জহির রায়হান পরিচালিত ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেয়া’ মুক্তি পায়।
শহীদ মিনার
ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যে জায়গায় প্রথম গুলি চলেছিল, সে জায়গায় নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার। নাম রাখা হয়, শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। যার উচ্চতা ছিল ১২ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট। নকশাকার ছিলেন বদরুল আলম। নির্মাণ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ভেঙে ফেলা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। প্রথম শহীদ মিনার বা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসের প্রতিবাদে কবিতা লেখা হয়, স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো। পুলিশের হাতে প্রথম শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতা।
শহীদ দিবস
১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো পালন করা হয় শহীদ দিবস। ওই দিন বিভিন্ন স্তরের ও শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা খালি পায়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে।